
আয়শা সিদ্দিকা
শেষ বিকেলের মেয়ে : মানব মনের জটিল ভাবনার শিল্পরূপ
অভিজ্ঞতা শব্দটি কাহিনী সাহিত্যের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। বাংলায় এ শব্দটি একটু বেশিই সম্পৃক্ত। বাংলার গল্প-উপন্যাস বিবেচনায় আমরা বারবারই জানতে চাই লেখকের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে কি না। অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বাংলাদেশের কথাসাহিত্যে দক্ষ সারথী জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭৯)। বাংলাদেশের উপন্যাসের উদ্ভব, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার নিরীক্ষাশীল ধারায় অবস্থান করে তিনি সময়, সমাজ ও জীবনাভিজ্ঞতার অভিব্যক্ত ওসধমব বা রূপকল্পের সমন্বিত রূপায়ণ করেছেন। শুধু সাহিত্যাঙ্গনে নয় কর্মচাঞ্চল্যে ভরপুর, ক্ষুরধার চেতনার অধিকারী জহির রায়হান পঞ্চাশের দশকে বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম সৃজনশীল ও প্রগতিশীল ব্যক্তিত্ব। কৈশোর থেকেই তাঁর সৃজনচর্চা শুরু। পরবর্তীতে সাহিত্যচর্চা, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ, পত্রিকা সম্পাদন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড নেতৃত্ব, প্রগতিশীল রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা, চলচ্চিত্র নির্মাণ ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ সর্বক্ষেত্রেই ছিলেন সক্রিয়। জাতির অন্যতম এই শ্রেষ্ঠসন্তান ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ আগষ্ট ব্রিটিশ উপনিবেশভুক্ত অভিভক্ত বাংলার প্রাচীন জনপদ বৃহত্তর নোয়াখালী অঞ্চলের ফেনী জেলার সোনাগাজী থানার মজুপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম আবু আবদার মোহাম্মদ জহিরুল্লাহ, ডাক নাম জাফর এবং কমরেড মণিসিংহ প্রদত্ত রাজনৈতিক নাম রায়হান। পিতা মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ, মাতা সৈয়দা সুফিয়া খাতুন। পিতা-মাতার অষ্টম সন্তানদের মধ্যে জহির রায়হান ছিলেন তৃতীয়। পারিবারিক ভাবেই তিনি রাজনীতি সচেতন হন। বাঙালি সত্তাসন্ধানী সংগ্রামের প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর অগ্রণী ভূমিকার মাধ্যমে যার প্রকাশ ঘটে ।
বিচিত্র জীবনসংঘাত ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামের মতোই তাঁর সাহিত্যশিল্প ছিল বর্ণাঢ্য আর বৈচিত্র্যে ভরপুর। দূর অতীত কিংবা দূর ভবিষ্যৎকে নিয়ে স্বপ্ন তৈরি না করে তিক্ত এবং বর্ণহীন বর্তমানকে চিত্রিত করেছেন শৈল্পিক ভাষায়। তাঁর রচিত গল্প বা উপন্যাসে শিল্পকে ছাপিয়ে জীবনই হয়ে উঠেছে প্রধান উপজীব্য। প্রতিটি সৃষ্টিকর্ম যেন জীবন থেকে নেয়া। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। ‘১৯৪৯ খ্রিষ্টাব্দে তিনি যখন হাই স্কুলের ছাত্র তখন কলকাতার ‘চতুষ্কোণ’ পত্রিকায় ‘ওদের জানিয়ে দাও’ শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।’১ পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাকালীন সময়ে প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হয় সূর্যগ্রহণ (১৯৫৫)। তাঁরা প্রথম একক পরিচালিত চলচ্চিত্র- কখনো আসেনি (১৯৬১)। এছাড়া অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের মধ্যে রয়েছে কাঁচের দেয়াল (১৯৬৩), সোনার কাজল (১৯৬২), সঙ্গম (১৯৬৪), বাহানা (১৯৬৫), বেহুলা (১৯৬৬), আগুন নিয়ে খেলা (১৯৬৭), আনোয়ারা (১৯৬৭), সুয়োরানী দুয়োরানী (১৯৬৮), বেদের মেয়ে (১৯৬৯), জীবন থেকে নেয়া (১৯৬৯), জ্বলতে সরুজ কী নিচে (১৯৭০), যোগ বিয়োগ (১৯৭০), লেট দেয়ার বি লাইট (১৯৭০-১৯৭১) অসমাপ্ত, স্টপ জেনোসাইড (১৯৭১), এ স্টেট ইজ বার্ন (১৯৭১)। তাঁর প্রথম উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে (১৯৬০)। অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে রয়েছে তৃষ্ণা (১৯৬২), হাজার বছর ধরে (১৯৬৪), বরফ গলা নদী (১৯৬৯), আরেক ফাল্গুন (১৯৬৯), আর কত দিন (১৯৭০), একুশে ফ্রেব্রুয়ারি (১৯৭০), কয়েকটি মৃত্যু (১৯৭০)। তাঁর প্রথম উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে একটি পঞ্চভুজ প্রেমকাহিনীর সার্থক শিল্পরূপ। তবে প্রণয় সম্পর্কের অন্তরালে সমাজ বিন্যস্ত মানবজীবনের বিচিত্র বাঁক ও অনুভূতি উপন্যাসের গাঠনিক মানদণ্ডে কতটুকু একীভূত হয়েছে তাই প্রবন্ধটির উপজীব্য বিষয়।
‘ব্রিটিশ বাণিজ্যশক্তি ও শিল্পশক্তির অভিঘাতে অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতাকেন্দ্রীক যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা ঘটে, বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মধ্যবিত্তের ইতিহাস তা থেকে স্বতন্ত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত কলকাতা শহর এবং মধ্যযুগের মুঘল শাসকবর্গ সৃষ্ট ঢাকা নগরী আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্যের কারণে গোড়া থেকেই স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশ লাভ করেছে।’২ এছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ-
পলাশির বিপর্যয় (১৭৫৭), চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩), সিপাহি বিদ্রোহ (১৮৫৭), কংগ্রেস (১৮৮৫) ও মুসলিম লীগ (১৯০৬) প্রতিষ্ঠা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও বিভেদের রাজনীতি, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রভৃতির প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব বাংলার জনজীবনে অপরিসীম। সামাজিক জীবনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যাঙ্গনের প্রতি শাখার মতো উপন্যাসেও এর প্রভাব অনস্বিকার্য। এ সময় সমাজ জীবনের জটিল ও দ্বান্দ্বিক চেতনা প্রবাহই ১৯৫৮-১৯৭০ কাল পর্বের উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে। ‘শোষণ-নিপীড়ন, প্রতিবাদ, রক্তক্ষরণ ও দ্রোহ এ পর্যায়ের সমাজ-চৈতন্যকে যেমন করেছে অস্থির ও দ্বন্দ্বরক্তিম তেমনি সমাজ বিকাশ-প্রক্রিয়ার বহুভুজ জটিলতা শিল্পীর আত্মপ্রকাশকেও করেছে তার অনুগামী। ব্যক্তি ও সমষ্টি অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটে বাংলাদেশের শিল্পীচিত্ত হয়ে উঠেছে উদ্বেগাকুল, জাতিসত্তার প্রশ্নে সতর্ক ও সন্ধানী এবং অভীপ্সার বিচিত্র রূপকল্প সৃজনে ঐকান্তিক।’ ৩ মূলত সামাজিক জীবন পটচিত্রের অন্তর-বাহিরের বৈপরীত্যময় সত্যের সমগ্রতা সন্ধানে সমাজকাঠামোর দ্বন্দ্বময় ক্রমবিকাশ, উপনিবেশ
শৃঙ্খলিত সমাজের জীবনকামী মানুষের আত্মসন্ধান, সত্তাসন্ধান ও জাতিসত্তা সন্ধানের জটিল রূপ সৃষ্টিই এখনকার রচিত উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য। আর এসব উপন্যাসের মধ্যে জহির রায়হানের শেষ বিকেলের মেয়ে অন্যতম। আপাতদৃষ্টিতে রোমান্টিক প্রেমকাহিনী হলেও ঔপন্যাসিক এখানে বাঙালির বিকাশমান মধ্যবিত্তের দ্বান্দ্বিপ জটিল ও বিবর্ণ মানসবৈশিষ্ট্য সূক্ষ্ম ও দক্ষভাবে চিত্রিত করেছেন। ‘কলোনি শাসিত সমাজের সময়দাস মধ্যবিত্তের স্বপ্নলালিত জীবন এ উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য।’৪
উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র কাসেদ সীমিত আয়ের কেরানি বাঙালি নি¤œ মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি। জীবনের মোড়ে মোড়ে বাধা প্রাপ্ত নিম্ন মধ্যবিত্তের স্বপ্নময় জীবন কল্পনা ও ভবিষ্যৎ ভাবনার স্বরূপ উন্মোচিত করেছে লেখক তার চরিত্রের মাধ্যমে। কাসেদের চরিত্রের সংবেদনশীলতার অতিরেক সৃষ্টির জন্য তার স্বভাব-বৈশিষ্ট্যে কবিত্বশক্তি আরোপ করেছেন। জীবনের দ্বন্দ্বমুখর নানান ঘটনাক্রমের মাধ্যমে উপন্যাসটির চরিত্র ও বর্ণনাশৈলী কতটা বাস্তবিক, সময়সিদ্ধ ও জীবনধর্মী এখন তাই দেখা যাক :
জহির রায়হানের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে তাঁর পরিবার থেকে, তাঁর সময় থেকে, তাঁর আপন সমাজ থেকে। তাঁর পরিবারটি ছিল প্রগতিশীল, রাজনীতি সচেতন, উদার, মানবিক সিগ্ধতায় ভরপুর। তাঁর অগ্রজ বামপন্থী রাজনীতিক, কথাশিল্পী ও সাংবাদিক। বড়বোনও ছিলেন রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর জীবনে তাঁদের প্রভাব অনেক। অন্যদিকে ষাটের দশকে পূর্ব বাংলায় ঘটে যাওয়া ভাষা আন্দোলন তাঁর সত্তাকে আমূল নাড়া দিয়েছে। এ আন্দোলন একদিকে তাঁকে সামাজিক যুগপৎ রাজনৈতিক ভাবে প্রভাবিত করেছে অন্যদিকে করেছে দায়িত্বশীল, করেছে দায়বদ্ধ। এছাড়া শাসক আইয়ুব খানের সময়ের সাম্প্রদায়িকতা, গণতন্ত্রহীনতা, শোষণ-নির্যাতন-অত্যাচার-জুলুম তাঁকে সোচ্চার কণ্ঠ তোলার সাহস জুগিয়েছে। ব্যক্তিগত এই অভিজ্ঞতা তাঁর প্রতিটি উপন্যাসে প্রতীয়মান, যার সূচনা ঘটে প্রথম উপন্যাস শেষ বিকেলের মেয়ে এর মাধ্যমে। এ উপন্যাসে যেমন এসেছে শ্রেণিচেতনা, সমাজ বৈষম্যের চিত্র, তেমনি অঙ্কন করেছেন দুর্বৃত্তের মুখাকৃতি, সুবিধাবাদীদের নগ্নমূর্তি এবং শোষিত, ভাগ্য-বিড়ম্বিত, দরিদ্র, নিঃস্ব, অসহায় মানুষের ছবি, এঁকেছেন লড়াকু, সংগ্রামী এবং মধ্যবিত্ত ভাবুক সাধারণ মানুষের প্রতিচিত্র। অন্যদিকে বলেছেন সদ্যজন্ম নেওয়া শহুরে মধ্যবিত্ত সমাজের কথা, তাদের আবেগ, জীবনের শাশ্বত বহমান বৈশিষ্ট্য, জাগতিক ভাবনা এবং শ্রেণিবাস্তবতার স্বরূপ। মূলত, ‘খ-িতভাবে, বিচ্ছিন্নভাবে নয়, সামগ্রিক মানবিক দৃষ্টিতে জহির রায়হান মানুষের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর উপন্যাসে। তিনি মানুষকে সামাজিক অবস্থানের প্রেক্ষিতে তার ভেতরকে দেখেছেন, বহিরাঙ্গিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চেতনার নিরিখেও বিচার করেছেন।’৫
সমাজচিত্র:
শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসটি কল্পনায় ভরপুর স্বপ্ন-আবেশে সাজানো। স্বপ্নের পাশাপাশি প্রকৃতির বর্ণনা এনেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন সমাজ অবক্ষয়ের চিত্র কিংবা বাস্তব-অবাস্তবের দ্বন্দ্বমুখর ছবি। তিনি দেখিয়েছেন সাধারণ নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনের কাক্সিক্ষত, প্রলুব্ধস্বপ্ন কেমন করে ফিকে হয়ে যায়। কেমন করে বিত্তবানেরা তাদেরকে ক্রীড়নক করে রাখে। স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যর্থ হলে কেমন করে দূরে ফেলে দেয়। কাসেদের সঙ্গে জাহনারার সামান্য খুনসুটীতেই কাসেদকে সে দূরে ঠেলে দেয় এভাবে-
শরীর খারাপ বলে নিচে নেমে এসে একবার কাসেদের সঙ্গে দেখাও করতে পারলো না জাহানারা? এর আগে জ্বর নিয়েও ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছে সে, কাসেদ নিষেধ করলেও আমল দেয়নি। কথাটা সহসা বিশ্বাস হতে চাইলো না ওর। চাকরটা মৃদু হেসে চলে গেলো ভিতরে। হাসলো না, যেন বিদ্রুপ করে গেলো ওকে। আবার একা। ঘরের মধ্যে বার কয়েক পায়চারি করলো কাসেদ। ভালো লাগছে না, বারবার করে মনে হলো, জাহানারা আজ ইচ্ছে করে অপমান করলো তাকে। সে কোন অপরাধ করে নি তবু তাকে শাস্তি দিলো জাহানারা। কাসেদের মনে হলো পুরো দেহটা জ্বলছে ওর।৬
এ উপন্যাসের পটচিত্র অঙ্কিত হয়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়ের প্রেক্ষাপটে। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেরও অবসান ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম নিদর্শন মধ্যবিত্ত সমাজের আবির্ভাব। পূর্ব বাংলায়ও তখন এ সমাজের আনাগোনা শুরু হয়েছে। এ উপন্যাসেও মধ্যবিত্ত সমাজের শিক্ষা সচেতনতা লক্ষ করা যায় যেমন আছে আবু জাফর শামসুদ্দীনের মুক্তি উপন্যাসে। সেখানকার নায়ক আশরাফ বিয়ের প্রথম রাতেই কনেকে প্রশ্ন করেছিল সে লেখা পড়া জানে কিনা। তেমনি এ উপন্যাসে কাসেদের খালু বৌ-এর লেখা পড়া প্রসঙ্গে বলেছে-
মা কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে হঠাৎ বললেন, নাহারের জন্যে একটা ছেলে দেখে দাও না। বয়স তো ওর কম হলো না।
খালু বললেন, আজকাল ছেলে পাওয়া বড় ঝকমারি বড়বু। ম্যাট্রিক পাশ করা ছেলে, সেও আবার ম্যাট্রিক পাশ মেয়ে চায় বুঝলেন না? মা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর অস্পষ্ট গলায় বললেন, মেয়ে আমার ম্যাট্রিক পাশ নয় সত্যি, কিন্তু ঘরকন্নায় ওকে কেউই হার মানাতে পারবে না। ক্ষণকাল নীরব থেকে মা আবার বললেন, কি যে হয়েছে আজকাল কিছু বুঝিনে, আমাদের জামানায় লোকে দেখতেন মেয়ে কেমন রান্নাবান্না করতে পারে। ‘সে জামানা পুরোনো হয়ে গেছে বড়বু।’এখন লোকে লেখাপড়া না জানা বউ এর কথা চিন্তাও করতে পারে না।৭
আবহমান কাল ধরে প্রচলিত হয়ে আসছে মেয়েদের অবস্থান সমাজের নীচের তলায়। তাইতো সীতার মতো বারবার অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেও সমাজ তাদের গুণ সম্পর্কে সন্দিহান। বিংশ শতাব্দীতে যখন চারিদিকে পরিবর্তনের জোয়ার এসেছে তখনও নারী ঘরের কোণে আবদ্ধ, মেকি পোশাকে হয়তো কোথাও কোথাও দৃশ্যমান হয় তবু আন্তর স্বাধীনতার ছায়া সে মাড়ায় নি। উপন্যাস উল্লেখিত সময়েও নারীর বিবাহ নিয়ে নানা জটিলতা দেখা যায়। নানা প্রতিবন্ধকতা বার বার তার অসহায়ত্বের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাইতো গৃহ কর্মে সুনিপুণা মেয়ে নাহার তার যোগ্য স্বামী পায়নি, পায়নি তার যোগ্য সম্মানটুকুও। এসব মেয়েদের অসহায়ত্বের বর্ণনা লেখক খালু ও মায়ের মুখে উচ্চারণ করেছেনÑ ‘খালু বললেন, আজকাল মেয়ে বিয়ে দেবার মত ঝকমারী আর নেই বড়বু। যাদের টাকা আছে তারা টাকা পয়সা নিয়ে ভালোভালো ছেলে বেছে নেয়। ....মা বললেন, আগের দিনে লোকে বংশ দেখতো। এখন সি. এস. পি ছাড়া দেখে না।’৮ এখানে শুধুমাত্র মেয়েদের অবস্থানই নয় সমাজে সহায়সম্বলহীন মানুষের জীবন মূর্তিও প্রতিফলিত হয়েছে। আধুনিক যুগে নারী স্বাধীনতা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক। তবে এ উপন্যাসে নারীদের মতামতের গুরুত্ব নেই বললেই চলে এমনকি তারা নিজেরাও সচেতন নয়। তাইতো মা কাসেদের কাছে নাহারের বিয়ের মত চাইলেন। কিন্তু কাসেদ তার বোনের মতামত জানতে চাইলে মা বলেন, ‘ওকে আবার জিজ্ঞেস করবো কি? মা চোখ তুলে তাকালেন ওর দিকে। আমরা কি ওর খারাপ চাই? ছেলেটা শুনছি দেখতে শুনতে ভালো।’ ৯ কাসেদ নাহারের মতামত জানতে চাইলে নাহার বিরক্ত ও বিতৃষ্ণা কণ্ঠে জানিয়েছে, ‘আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করবেন, আমার কোন মতামত নেই।’ ১০
মধ্যবিত্ত সমাজের যৌতুক প্রথা বাস্তব সত্য ছিল, বাংলাদেশের সমাজে তো বটেই। এ উপন্যাসেও সমাজের এ দিকটি ফুটে উঠেছে মকবুল সাহেবের পারিবারিক বর্ণনায় ‘একবার এই অফিসের একটি ছেলেকে নাকি জামাতা বানাবার কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন তিনি। ......কিন্তু বিয়ে হলো না। ছেলেটি রাজী হলো না বিয়ে করতে। কেন? কেউ জানে না। শুধু জানে, ছেলেটি নাকি মকবুল সাহেবের কাছ থেকে কিছু নগদ কড়ি দাবি করেছিলো।’১১
একটি সমাজে ভাল-মন্দ সবারই সমাগম থাকে। এ উপন্যাসে যেমন সহজ সরল মানুষের নিত্য নৈমিত্তিক কাজের বিবরণ, তাদের আচারণ প্রতিফলিত হয়েছে, তেমনি কিছু কঠিন ও জটিল মানুষের পরিচয়ও পাওয়া যায়, যারা বিচরণ করে উপরি খাওয়ার লোভে, নিজ স্বার্থ চরিতার্থে তারা অন্যায় করতেও দু’বার ভাবে না। এমন শ্রেণির মধ্যে রয়েছে শিউলি ও জাহানারা। শিউলির সঙ্গে কাসেদের দেখা হয় জাহানারাদের বাড়ি। শিউলি বড়লোক, চঞ্চল ও সুবিধাবাদী। তার প্রেমিক থাকে ইতালিতে। তাই সময় কাটানোর জন্য বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা পাওয়ার জন্য সরল প্রাণ কাসেদ ব্যবহার করে। অন্যদিকে সে যখন জানতে পারে জাহানারার সঙ্গে কাসেদের সুসম্পর্ক রয়েছে প্রায় প্রেমের কাছাকাছি তখন ঈর্ষান্বিত হয়ে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে উভয়ে সম্পর্কে দুরত্ব তৈরি করে। শিউলি বলে- এখনো বুঝলেন না? ঠোঁট টিপে আবার হাসলো সে এই সহজ কথা বুঝতে দেরি হচ্ছে আপনার? চারপাশে এক পলক দেখে নিয়ে আরো কাছে সরে এলো শিউলি। মাস্টার আর ছাত্রীতে মন দেয়া নেয়ার পালা চলছে, বুঝলেন?’১২ অন্যদিকে কাসেদ যখন শিউলির কাছে নিজেকে সমার্পণ করতে চাইল তখন তার মায়াজালে বিদ্ধ কাসেদের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে ফেলল। লেখকের বর্ণনায়-‘কাসেদের বুঝতে আর বিলম্ব হলো না সন্ধেবেলার এই শিউলির সঙ্গে সকালের সেই শিউলির কোন মিল নেই। এরা যেন দু’টি ভিন্ন মেয়ে। সম্পূর্ণ আলাদা।’১৩ শিউলির মতো জাহানারার চরিত্রেও এমন বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।
তৎকালীণ সময়ে হিন্দু-মুসলিম নর-নারীর বিবাহ সমাজ স্বীকৃত না হলেও অনেক ঔপন্যাসিক হিন্দু মুসলিম নর-নারীর বিবাহ বন্ধনকে উপন্যাসের উপাত্ত করে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ঘটিয়েছেন। কিন্তু তখনকার সময়ের উপন্যাসে নাগরিক জীবনে প্রেমের ঘটনা বহুল প্রচলিত ছিল না। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মুসলমান পরিবারের নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ ছিল খুবই সামান্য, তাকে মনে করা হতো অন্যায় ও গর্হিত। সালমা নারী পুরুষের বন্ধুত্বকে কটাক্ষ করে বলেছে, ‘আগের দিনে ছেলের সঙ্গে ছেলের বন্ধুত্ব হতো। মেয়েদের সঙ্গে মেয়ের। আজকাল ছেলেতে মেয়েতে বন্ধুত্বের পালাটা বড় জোরেশোরে শুরু হয়েছে। ...বন্ধুর স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী, নিজের স্ত্রীকেও বলি বান্ধবী। বন্ধুর প্রেমিকা, তাকেও ডাকি বান্ধবী বলে আবার নিজের প্রেয়সী তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলি, বান্ধবী।’১৪ মূলত সে সময় নারী-পুরুষের মেলামেশা পূর্ববাংলার সমাজ কাঠামোয় ব্যাপকভাবে প্রত্যক্ষিত না হওয়ায় শুধু সমাজের চোখে নয়, নিজেদের মধ্যেও এমনকি তরুণ যুবকদের মধ্যেও সংকোচ কিংবা অস্বস্তির সৃষ্টি করত। এ সম্পর্কে কাসেদ ও শিউলি এক সঙ্গে রিকশায় বসার ঘটনা উল্লেখযোগ্য। অপরিচিত কোন মেয়ের সঙ্গে রিকশায় চড়ার অভিজ্ঞতা কাসেদেও সেটাই প্রথম। লেখকের বর্ণনায়- “তাই বারবার অস্বস্তিবোধ করছিলো কাসেদ। কপালে মৃদু ঘাম জমছিলো এসে, বারবার ওর কাছ থেকে সরে বসার চেষ্টা করছিল সে।”১৫ এ ঘটনাক্রমের মধ্য দিয়ে মূলত ঔপন্যাসিক সমাজ পরিবর্তনের চিত্রকেই অঙ্কন করেন।
সমাজের বহুল পরিচিত আর একটি বিষয় পরচর্চা। এখানকার অনেক চরিত্রে এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। আপন কর্ম ফেলে, দুর্বলতা ভুলে গিয়ে কিছু চরিত্র অন্যের ত্রুটি খুজে বেড়ায়। উপন্যাসে এমন চরিত্রের মধ্যে রয়েছে বড় সাহেবের কোম্পানির লোকেরা। অফিসের কর্ণধার হলেও বড় সাহেবের সমালোচনা করতে কোম্পানির লোকেরা পিছু পা হয় নি। সামনে বলার সাহস নেই তবে তার অবর্তমানে, তাঁর মুখরোচক সমালোচনায় মুখর থাকে অফিস রুমগুলি। মকবুল সাহেব অসুস্থ হলে তার সেবা শুশ্রুষার দায়িত্ব নিলে তারা সমালোচনা করে এভাবে- ‘একাউনটেন্ট তার টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে বলেন, পরশু দিন বিকেলে দেখলাম বড় সাহেব তাঁর গাড়ি করে ওদের হাসপাতাল থেকে বাসায় পৌঁছে দিচ্ছেন।’১৬
এছাড়া ঔপন্যাসিক এ উপন্যাসে তৎকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তের বসতঘর এমনকি আসবাব পত্রের খবর পর্যন্ত উল্লেখ করেছেন। রাজধানী ঢাকা নগরীর নতুন এলাকায় সদ্য চুনকাম করা বিত্ত, বৈভব ও প্রাচুর্যেভরা অট্টালিকার পাশাপাশি অন্ধকারের মতো পুরোনো ঢাকার বিবরণ দিয়েছে। বিধৃত করেছে নি¤œ মধ্যবিত্তের সাংসারিক অভাব দৈন্যকেও। বর্ণিত আছে, ‘লালবাগে একটা সরু গলির ভেতরে একখানা আস্তর উঠা একতলা দালান আর একটা দোতলো টিনের ঘর নিয়ে থাকেন মকবুল সাহেব। বড় পরিবার, ছেলে, মেয়ে, নাতি, নাতনি। বাইরের একখানা ঘর বৈঠকখানা এবং স্কুল পড়–য়া দুই ছেলের শোবার ঘর হিসেবে ব্যবহার করছেন তিনি। ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রের চেয়ে ধুলোবালি আর আবর্জনার আধিপত্য সবার আগে চোখে পড়ে।’১৭ এভাবে ১৯৪৭ পরবর্তী ঢাকা শহরে সদ্য অঙ্কুরিত নাগরিক জীবন, অর্থনৈতিক কাঠামো, এবং নগরায়ণের নানা উপাচারে সাজিয়ে তুলেছেন শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসের বাণীবুনন।
মধ্যবিত্তের দ্বান্দ্বিক অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা :
উপন্যাসের স্রষ্টা মধ্যবিত্ত শ্রেণি, তবে বাংলাদেশের উপন্যাসে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে মধ্যবিত্ত জীবনের
রূপায়ণ বিলম্বিত হয়েছে। বিভাগোত্তর কালে সামন্ত মূল্যবোধ আশ্রয়ী মধ্যবিত্ত শ্রেণি পাকিস্তান রাষ্ট্রের সহযোগী শক্তিতে পরিণত হওয়ায় বুর্জোয়া মতাদর্শে বিশ্বাসী ও পুুঁজি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বাবলম্বন প্রত্যাশী মধ্যবিত্তের বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভেতরে ভেতরে তাদের মানসিকতা জটিল থেকে জটিলতর হয়। আর ১৯৫৮-১৯৭০ কালপর্বের উপন্যাসে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত মানসের সেই সামূহিক অস্তিত্বগত সংকটের আদ্যপান্ত রূপায়ণ করা হয় ।
বঙ্গদেশে নাগরিক সভ্যতার যুগ মুঘল আমল থেকে শুরু হলেও বাংলায় আধুূনিক নগর জীবনের শুরু ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সূচনা লগ্নে। ১৮৫৭ সালে সেপাহি বিদ্রোহের পর বাংলাদেশে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে। শুরু হয় ব্রিটিশ সা¤্রাজ্যের শাসন । মূলত ব্রিটিশ শাসনের শুরু হয় শিল্পতান্ত্রিক ধনতন্ত্রের সূচনার মধ্য দিয়ে। আর ভারত বর্ষের তথা বাংলার রাজনৈতিক পট পরিবর্তনে, অর্থনৈতিক পরিবর্তনে, নগর জীবনও সংস্কৃতির রূপান্তরে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের ভুমিকা ষ্মরণযোগ্য। ‘ঊনিশ শতকের বাঙ্গালি রেনেসাঁ বা নগজাগরণ মুলত পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতার সম্ভোগের ফল।’১৮ প্রথম ইতালির ফ্লোরেন্সে এই নবজাগরণের সূচনা ঘটে। মধ্যযুগীয় স্থবির জীবন থেকে মোহমুক্তি, সামন্তসমাজ থেকে ধনতান্ত্রিক সমাজে উত্তরণ,নগরের অর্থনৈতিক শ্রেণিবিন্যাসে স্বাধীনতা অর্জনই ছিল এ আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। যা পরবর্তীতে বাঙালি সমাজে সংযুক্ত হয় ব্রিটিশ শাসনকালে। প্রথম দিকে হিন্দু সম্প্রদায় নব চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়। তবে ‘জাতীয় জীবনে এ সময়ে যে আধুনিকতার সূত্রপাত ঘটেছিল। তার সবটাই ছিল আরোপিত।’১৯ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামের সূচনালগ্ন থেকে আবর্তিত হয় মুসলিম নাগরিক নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি। সামাজিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে আবার তারা সাহিত্যেও ঠাঁই করে নিয়েছে। ‘১৯৪৭-১৯৫৭ কালপর্বে রচিত উপন্যাসে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন সংগঠনের বিচিত্র রূপ এবং উদ্ভিন্নমান মধ্যবিত্ত জীবনের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে।’ ২০ পরবর্তীতে ১৯৫৮-১৯৭০ কালপরিসরের উপন্যাসে তা আরও মাত্রা বহুল হয়েছে। নি¤œ মধ্যবিত্ত শ্রেণির আচারণগত বৈশিষ্ট্য হল- অস্তিত্বশঙ্কা, আতœমগ্নতা, পলায়ণপরতা ও মনস্তাপে বিদীর্ণ-বিচুর্ণ জীবনানুভূতি, গ্রামীণ জীবন পেরিয়ে নাগরিক শিক্ষা, রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গির রূপায়ণ, ইতিহাস সচেতনতা প্রভৃতি। এখন শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসে নাগরিক নি¤œ মধ্যবিত্ত সত্তা কতটুকু ধারণ করেছে তাই দেখার বিষয়।
রাজনীতি মধ্যবিত্তের জীবনের অবিচ্ছিন্ন অংশ। এ উপন্যাসেও আমরা রাজনীতির স্পর্শ লক্ষ করি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর প্রতিবেশে নি¤œ মধ্যবিত্ত জীবনের প্রণয় উপাখ্যান বিধৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে। কাসেদের জীবনের সবচেয়ে নীরব নায়িকা নাহারের পরিচয় দিতে গিয়ে ঔপন্যাসিক যুদ্ধ পরিস্থিতি বর্ণনা করেছেন।
কাসেদের আপন বোন নয় নাহার।
মায়ের দূর সম্পর্কের এক খালাতো বোনের মেয়ে। ছোটবেলায় ও র মা মারা যান। ওর বাবা তখন কি একটা কোম্পানিতে চাকরি করতেন।
.....কিছুদিন পরে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে মিলিটারীতে চলে যান। নাহারকে রেখে যান মায়ের কাছে। মাঝে মাঝে চিঠি আসতো।
কখনো মাদ্রাজ থেকে। কখনো পেশোয়ার থেকে। কখনো কানপুর। শেষ চিঠি এসেছিলো আরাকান থেকে।
তারপর তার আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় নি।
কেউ বলেছে যুদ্ধে মারা গেছে।
কেউ বলেছে, জাপানীরা ধরে নিয়ে গেছে টোকিওতে। লড়াই শেষ হলো।
সন্ধি হলো শত্রু-মিত্রে।২১
মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের সব কিছুতেই অতৃপ্তি। জীবনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে নিজেরাই ভুলে যায় তারা কী চায়, কী তাদের প্রাপ্য। তাইতো এ শ্রেণির মানুষের চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকে অপূর্ণতা, সর্বক্ষণ অস্থিরতা গ্রাস করে থাকায় জীবনের পূর্ণার্থের সন্ধান মেলেনা কখনো। তাইতো শিউলি কোনটি সঠিক, কোনটি সত্য তা বুঝতে অপারগ। তার চাওয়া আর প্রাপ্তির মধ্যে রয়েছে ভিন্নতা। শিউলির উক্তিতেই তা প্রত্যক্ষিত, ‘চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সাপে-নেউলের সম্পর্ক রয়েছে যে। এই দেখুন না, আমি চাই ছেলেদের সঙ্গে বন্ধু হিসেবে মিশতে আর ওরা চায় আমাকে ঘরের গীন্নী হিসেবে পেতে। ভাবুন তো কেমন বিচ্ছিরি ব্যাপার।’২২
উপন্যাসটি রোমান্টিক প্রেমের গল্প হলেও ‘উপন্যাসিক বিকাশমান বাঙ্গালি মধ্যবিত্তের দ্বন্দ-জটিল ও বিবর্ণ অবস্থাকে সুক্ষ্মভাবে এ উপন্যাসে রূপায়িত করেছেন। কলোনিশাসিত সমাজের সময়দাস মধ্যবিত্ত স্বপ্নললিত জীবন এ উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য।’২৩ সাধারণত নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবনের কাক্সিক্ষত-প্রলুদ্ধ স্বপ্ন চিরদিনই অপূরনীয়। তাই তারা ভর করে কল্পনায়। বাস্তবতার শূন্য কোটর থেকে কল্পনার আবেশে সুখ অনুভব করে। উপন্যাসের নায়ক কসেদ সেই প্রকৃতিরই। স্বপ্নই তার অবলম্বন। দুচোখ ভরা তার কল্পনা । যে মেয়েকে দেখে, তাকেই তার ভালো লাগে। কাসেদের অবস্থান নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে। কল্পনাপ্রবণ কাসেদের স্বপ্ন খুব বড় নয়, লোভনীয় নয়, বিত্ত-বৈভরের নয়, যেন-তেনভাবে টাকার পাহাড় গড়া নয় তার স্বপ্ন সামান্য, সুখী-ছোট্ট সংসারের, ‘জানালার পাশ থেকে সরে এসে বিছানায় বসলো কাসেদ। ওর মনে এখন রঙের ছোঁয়া লেগেছে। দুচোখে স্বপ্নের আবির ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে। একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ।’২৪ তবে তার এ ভাবনা কোন দিন আলোর মুখ দেখেনি। সে সংশয়ে ভুগেছে, দ্বন্দ্বে অস্থির মন কাতর হয়েছে। পায়নি কোন স্বস্তি, নিজের ভেতরের আন্তর্দ্বন্দ্বে প্রতিনিয়ত জর্জরিত হয়েছে। কাসেদের স্বগোক্তি এমন, ‘জাহানারা, এভাবে আর কতদিন চলবে বলতে পারো? কতদিন আমি ভেবেছি আমার মনের একান্ত গোপন কথাটা ব্যক্ত করবো তোমার কাছে। বলবো সব। বলবো এসো আমরা ঘর বাঁধি। তুমি আর আমি। আমরা দুজনা, আর কেউ থাকবেনা সেখানে। কেউ না।’২৫
তবে তার আশা কোনদিন পূর্ণ হয়নি। মধ্যবিত্তের স্বাদ এমনই হয়। এভাবেই ব্যর্থতার গ্লানিতে নিম্ন মধ্যবিত্তের চরিত্রেযুক্ত হয় অস্তিত্বের সংকট। দ্বন্দ্বমুখর পরিবেশে দাঁড়িয়ে বার বার ভুল, করে যেমনটি করেছে কাসেদ। এক নারীর প্রণয় ভিক্ষা চেয়ে ব্যর্থ হয়ে আশ্রয় পেতে চেয়েছিল অন্য এক নারীর আঁচল তলে । তবে সেখানেও ঠাঁই মেলে নি। পলায়ণপর ও মনস্তাপে বিদীর্ণ-বিচুর্ণ কাসেদের জীবনানুভূতি শেষ পর্যন্ত এমন, ‘প্রথম পরাজয়ের গ্লানি মুছে যাবার আগেই দ্বিতীয় বার পরাজিত হলো সে। নিজের বোকামির জন্যে নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো ওর। আগুনে হাত বাড়ালে পুড়বে জানতো। তবু কেন সে এমন করলো?’২৬
শেষ পর্যন্ত কাসেদের পিছুটানের মধ্যদিয়ে ঔপন্যাসিক নি¤œমধ্যবিত্তের পরাজিত মনকে বিধৃত করেছেন। কাসেদের মতো মধ্যবিত্তের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কোনদিন পিছু ছাড়ে না। প্রত্যহ কুরে কুরে নিঃশেষ করে তবু পারিপার্শ্বিক ঘটনা মোকাবেলার শক্তি ও সাহস কোনদিনই যোগান দিতে পারেনা । মূলত ঔপন্যাসিক দক্ষ হাতে নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন বৃত্তান্ত যথাযথ ভাবে চিত্রিত করেছেন এ উপন্যাসে।
চরিত্র চিত্রণ :
প্লট কিংবা ঔন্যাসিকের মতামতের মতো উপন্যাসে চরিত্রের যথার্থ রূপায়ণ সমান গুরুত্ববাহী। শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসে জহির রায়হান জীবনের একই বৃত্তে আবর্তিত গুটিকতক মানব-মানবীর আংশিক ঘটনাক্রমকে বিন্যাস্ত করেছেন। তাঁর এ উপন্যাসের চরিত্রগুলি অত্যন্ত সাদা-সিধে। তাদের কারো মধ্যে ক্ষমতার দাম্ভিকতা নাই, চারিত্রিক জৌলুস নাই, দার্শনিক ভাবপ্রবণতা নাই বরং নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের অলিতে গলিতে হেটে চলা অতি চেনা পথিকগুলিই তাঁর উপন্যাসের চৌকাটে ঢুকে পড়েছে। জীবন সংগ্রামে যুদ্ধরত বেশকিছু নর-নারীর আত্ম প্রচেষ্ঠাই মুখ্য হয়ে উঠেছে চরিত্রগুলোতে। উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র তথা নায়ক হলো কাসেদ। বড় সাহেবের কোম্পানীর একজন সামান্য করণিক, অল্প সয়স, পুরোনো ঢাকার কলতা বাজারে বসবাস করা এক রোমান্টিক যুবক। বাবা অনেক আগে মারা গেছেন। মা আর এক দুঃসম্পর্কের বোন নাহারকে নিয়ে তার সংসার। কাসেদ কল্পনাপ্রবণ মানুষ। অন্যদিকে, সংবেদনশীলতার অতিরেক সন্নিবেশ ঘটাতে লেখক তাকে কবি হশেবে উপস্থাপন করেছেন। ‘এ কারণেই জীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও কাসেদ কল্পনা চারিতায় আকাশস্পর্শী।’২৬ স্বপ্নই তার অবলম্বন। দু’চোখ ভরা তার কল্পনা এমন-
একদিন জাহানারাকে বিয়ে করবে কাসেদ। অর্থের প্রতি তার লোভ নেই। একগাদা টাকা আর অনেকগুলো দাসীবাদীর স্বপ্নও সে দেখে না। ছোট্ট একটা বাড়ি থাকবে তার, শহর নয়, শহরতলীতে, যেখানে লাল কাঁকরের রাস্তা আছে আর আছে নীল সবুজের সমারোহ। মাঝে মাঝে দু’পায়ে কাঁকর মাড়িয়ে বেড়াতে বেরুবে ওরা। সকাল কিম্বা সন্ধ্যায়। রাস্তায় লোকজনের ভিড় থাকবে না। নিরালা পথে মন খুলে গল্প করবে ওরা কথা বলবে।২৭
তার কল্পনার আকাশ সুবিশাল দিগন্ত বিস্তৃত। হৃদয় অকপট, উদার, মানবিক গুণসম্পন্ন লাজুক প্রকৃতির। অন্যদিকে সে ছিল নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি, যার জীবনে ছিল নানা প্রতিবন্ধকতা। লেখকের বর্ণনায় -
রাস্তায় এক হাঁটু পানি জমে গেছে। অতি সাবধানে হাঁটতে গিয়েও ডুবন্ত পাথর-নুড়ির সঙ্গে বারকয়েক ধাক্কা খেয়েছে কাসেদ। আরেকটু হলে একটা সরু নর্দমায় পিছলে পড়তো সে। গায়ের কাপড়টা ভিজে চুপসে গেছে। মাথার চুলগুলো বেয়ে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝরছে। শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন বাসায় এসে পৌঁছলো কাসেদ, তখন জোরে বাতাস বইতে শুরু করেছে।
বোধ হয় ঝড় উঠবে আজ। ২৮
এই ধাক্কা বা হোচোট খাওয়া শুধু প্রাকৃতিক নয় এটা তার জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তাঁর জীবনের প্রতিটি বাঁকে রয়েছে বাঁধা, না পাওয়ার যন্ত্রণা,স্বপ্নের অপূর্ণতা। আর এ ঝড় শুধুমাত্র প্রকৃতিগত নয় এই ঝড় কাসেদের জীবনের ঝড়ও বটে। তার মানসিকতার ঝড়কেও লেখক উপন্যাসের প্রথমে এভাবে আভাস দিলেন। মধ্যবিত্তের অন্যতম লক্ষণ ব্যক্তিত্বশীলতা। জীবনের নগ্নবাস্তবতায় দাঁড়িয়েও সে তার ব্যক্তিত্বের কাছে ছোট হয়নি। তাইতো সালমা যখন তাকে প্রশ্ন করে, যাবার জন্যে অমন হন্যে হয়ে উঠেছে কেন? তখন সে ব্যক্তিত্বপূর্ণ উত্তর দেয়- ‘চিরকাল থাকবো বলে আসিনি নিশ্চয়। কাজে এসেছিলাম, সারা হলো চলে যাচ্ছি।’২৯
মানুষ মাঝে মাঝে অনেক কিছুভাবে। কখনো তার অর্থ খুঁজে পায়, কখনো পায় না। তবু তার ভাবনার শেষ নাই। কাসেদও কল্পনা করেছে একদিন জাহানারাকে নিয়ে সুখের ঘর বাঁধবে। কিন্তু পূর্ণ হলো না তার সে স্বপ্ন। কপট আর ভ-ামির বণ্যায় ভেসে গেল তার স্বপ্ন। সে দিন হয়তো আকাশে অনেক তারা জ্বলেছিল, রাস্তায় অনেক লোকও ছিল। হয়তো বাতাসে কোন বাগানের মিষ্টি গন্ধ ভেসে এসেছিল। কিন্তু তার কোন কিছুতেই কাসেদের শূন্যতা পূরণ হল না। জাহানারার অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কের কথা ভেবে তার বিদীর্ণ হৃদয়ের রক্তক্ষরণ এমন-
জাহানারা, কেন এমন করলে তুমি ?
তোমাকে ভালবেসে পরিপূর্ণ ছিলাম আমি। যে দিকে তাকাতাম ভালো লাগতো আমার। আজ আকাশের নীল আর নিওনের আলো সবকিছু বিবর্ণ মনে হচ্ছে আমার চোখে।৩০
মানুষের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশার পরিণাম এমনই হয়। মধ্যবিত্ত মানুষের আর একটি বৈশিষ্ট্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা। কাসেদের বেলায়ও তাই। সে স্বপ্ন দেখেছে। ‘বাস্তবতা এর ভিন্ন। তবুও কল্পনার রোগে ছাড়ে না। বাস্তবতা বোধ যাদের নেই, শ্রেণি সচেতনতাবোধ যারা লালন করে না, তাদের মনের অলিন্দ থেকে কল্পনা সহজে বিদায় নেয় না। কাসেদ তেমনি এক যুবক, যার আছে স্বপ্ন দেখার রোগ।’৩১ কল্পনার আধিক্য থাকায় সে সিদ্ধান্ত নিতে পারে নি। বারবার ব্যর্থ হয়েছে। তার মানসিকতা এমন-
যা হবার হোক ।
জীবনে একটা চরম সিদ্ধান্ত নিতে চায় সে। জাহানারাদের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর মনে হলো কে জানে হয়তো আজ এখানে এই শেষ আসা।৩২
এমন ভাবনায়ও সে দৃঢ় থাকতে পারে নি। পারে নি জাহানারাকে মনের কথা বলতে । তাইতো দ্বিধা দ্বন্দ্বে দিকভ্রান্ত হয়ে সে নিজেকে শিউলির কাছে সমার্পণ করতে চায়। কিন্তু সেখানেও পরাজিত হয়। অবশেষে শেষ বিকেলের শান্ত শিষ্ট মেয়ে নাহারই তাকে আশ্রয় দান করে।
জাহানারা ও শিউলি এ উপন্যাসের অন্যতম চরিত্র। বড়লোকেরা যে সুবিধাবাদী হয় তার উত্তম উদাহরণ চরিত্র দুুটি। জাহানারা নিজের সুবিধার বা প্রয়োজনে কাসেদকে ব্যবহার করে। অন্যদিকে তার কাজিন শিউলিও বড়লোক, চঞ্চল, কপট এবং সুবিধাবাদী। তার প্রেমিক থাকে ইটালিতে তাই সময় কাটানোর জন্য বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা পেতে কাসেদের স্মরণাপন্ন হয়। তবে দু’জনেই ঈর্ষাকাতর। তাইতো জাহানার সঙ্গে কাসেদের মধুর সম্পর্কে ফাটল ধরাতে মিথ্যা কথা বলে। জাহানারাও ঈর্ষান্বিত হয়ে কাসেদের বাড়ি গিয়ে শিউলির প্রেমিকের কথা বলে দেয়। লেখকের ভাষায়- ‘কে জানে হয়তো এখন জাহানার একটা মনগড়া ব্যাপার। নিজে থেকে হয়তো একটা সিদ্ধান্ত টেনেছে সে। আর তাই নিয়ে ছুটে এসেছে কাসেদকে বলতে।’৩৩ অন্যদিকে কাসেদ যখন শিউলিকে বিয়ে করার অনুরোধ জানালো তখন শিউলি তার সুবিধাবাদী, ভ-ামি চরিত্র উম্মোচন করে বলেছে-
কাসেদের দিকে চমকে তাকালো শিউলি। অনেকক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর ধীরে ধীরে বললো, আমার দিক থেকে যদি কোন অন্যায় হয়ে থাকে তাহলে তার জন্যে আমি মাফ চাইছি কাসেদ সাহেব।
সত্যি আমি অপারগ, নইলে-।
কথাটা শেষ করলো না সে।
কাসেদের মনে হলো শিউলি হাসছে।
তীক্ষ্ম বিদ্রুপে ঠোঁটের কোণ জোড়া জ্বলছে ওর।
কাসেদ হেরে গেলো।৩৪
এ দুটি চরিত্রকে জহির রায়হান ব্যক্তি বা বিচ্ছিন্ন চরিত্ররূপে গড়ে তোলেন নি বরং ঢাকা নগরীর উঠতি ধণিক শ্রেণির অবস্থাকে তুলে ধরতে তাদের সৃষ্টি করেছেন।
এ উপন্যাসের সালমা হৃদয়হীনদের খপ্পরে পড়েছে। প্রথম দিকে কাসেদকে ভালবাসলেও কাসেদ তাকে পাত্তা দেয় নি। অন্য দিকে বিয়ের পর তার স্বামীও তাকে মূল্যায়ণ করে না। তাইতো ঔপন্যাসিক তাকে কিছুটা প্রতিবাদী করে তুলেছেন। যে সময় নারীদের ঘরে থাকাটাই সমাজের কাম্য, তাদের মতামত জানানোর স্থান বড়ই সংর্কীণ, সেই সময় সমাজ চোখে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে বিয়ের পর এক সন্তানের জননী হয়েও কাসেদকে নিয়ে পালানোর প্রস্তাব দিয়েছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়, ‘সালমা নীরবে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো ওর দিকে। ওর ঠোঁটের কোণে মৃদু মৃদু হাসি। তারপর টেনে টেনে বললো, আজ ; এখান থেকে বেরিয়ে, তুমি আমাকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারবে দূরে বহু দূরে কেথাও?’৩৫
কাসেদ তাঁর অপারগতা জানালে সালমার স্বপ্নগুলো কাঁচের ঘরের মতো বিচূর্ণ হয়ে গেলো। এ উপন্যাসের বৃদ্ধ কেরানি মকবুল আহমেদ। থাকেন পুরানো ঢাকায়। ছাপোষা মানুষ, কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা। চালাকি করে কাসেদকে নিয়ে গিয়েছিলেন বাসায় তাঁর মেয়ে বিয়ে দেয়ার জন্য। মধ্যবিত্ত সমাজের এক বাস্তবতা যেভাবে হোক মেয়ের বিয়ে দিতে হবে, মকবুল সেই বাস্তবতার প্রতিনিধি। লেখকের বর্ণনায়- ‘লোকে বলে বাসায় নেমন্তন্ন করার পেছনে নাকি কন্যাদায় মুক্ত হওয়ার একটা গোপন আকুতি রয়েছে।’৩৬
অন্যদিকে আর একটি চরিত্র কাসেদের অফিসের বড় সাহেব। প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে সে সুখী হতে পারে নি। তাকে ডিভোর্স দেয়। বিয়ে করে মকবুল সাহেবের মেজ মেয়েকে। ছোট্টকালে দরিদ্র ঘরের সন্তান হওয়ায় সে অনেক কষ্টে মানুষ হয়েছে। অনেক পরিশ্রমের মাধ্যমে জীবনে বড় হয়েছে। বৈবাহিক জীবনের প্রথমে অসুখী থাকলেও মকবুল সাহেবের মেজ মেয়েকে নিয়ে মধুর সংসার গড়ে। তার সম্পর্কে বর্ণিত আছে, ‘তবু কোনদিন দমে যাননি বড় সাহেব। হতাশা আসতো মাঝে মাঝে, তখন চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতেন তিনি। কান্না পেতো, কাঁদতেন , চোখের পানি ধীরে ধীরে চোখেই শুকিয়ে যেতো।’৩৭
এ উপন্যাসে কাসেদের মা ও বাবা দুটি বিপরীতমুখী চরিত্র। লেখক মাকে দেখিয়েছেন আবহমান বাংলা ও বাঙ্গালি সমাজে চিরপরিচিত ধর্মপ্রাণ মাতৃবতী রূপে। অন্যদিকে পিতাকে দেখিয়েছেন সমাজ সচেতন, প্রখর যুক্তিবাদী, ধর্মকর্ম সম্পর্কে অনাস্থাবাদী, আত্মপ্রত্যয়শীল মানুষ রূপে। এ দুটি চরিত্রই সমাজের অতি পরিচিত মুখ। কাসেদের মা সম্পর্কে বলা হয়েছে-
পাশের ঘর থেকে মায়ের কোরান শরীফ পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। টেনে টেনে সুর করে পড়ছেন তিনি। রোজ পড়েন। সকালে, দুপুরে আর রাতে। মাসে একবার করে কোরান শরীফ খতম করা চাই নইলে উনি শান্তি পান না। রাতে ভাল করে ঘুমও হয় না তাঁর।৩৮
আর বাবার সম্পর্কে বর্ণিত আছে-
‘বাবা ছিলেন একেবারে উল্টো মেরুর মানুষ। ভুলেও কোনদিন ধর্ম-কর্মের ধার ধারতেন না তিনি। এক বেলা নামাজ কিম্বা একটা রোজাও কখনো রাখেন নি। মা কিছু বলতে গেলে উল্টো ধমকে উঠতেন, বলতেন ওসব বাজে কাজে সময় ব্যয় করার ধৈর্য্য আমার নেই।’৩৯
এ উপন্যাসের অন্যতম একটি চরিত্র নাহার। নায়কের দূরসম্পর্কের আত্মীয়। এমনকি উপন্যাসটির নামকরণ ও হয়েছে তাকে কেন্দ্র করে। উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। তবে তা ছিল নিরবে, নিভৃতে, বাণীহীনভাবে। সে নিজেকে মগ্ন রেখেছে সাংসারিক কাজে। সমাজের জটিল-কঠিন বক্তব্যের বাইরে। তার নির্লিপ্ততাতেই যেন মুখরিত হয়েছে উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্র। চঞ্চল, কপট, প্রতিবাদী, উশৃঙ্খল চরিত্রের পাশে তাকে স্থান দিয়ে ঔপন্যাসিক মহিমা, সরলতা, স্নিগ্ধতাকেই উম্মোচন করে তাকে শ্রেষ্ঠ করে তুলেছেন। সে নিঃশব্দে কাসেদের ধ্যান করেছে, হৃদয়ে লালন করেছে ; যার উগ্র বা সচেষ্ট প্রকাশ ছিল না, কিন্তু তার প্রেম হৃদয়ে বিকাশমান ছিল। তাইতো বিয়ের পিঁড়ি থেকে উঠে এসেছে কাসেদের কাছে। বর্ণিত আছে-
কোন কথা না বলে নিঃশব্দে ভেতরে এলো নাহার । তারপর আলতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, এতকাল যার সাথে ছিলাম, তাকে ছেড়ে থাকতে পারলাম না বলে চলে এসেছি। যেতে বলেন তো আবার চলে যাই। কাসেদ বিস্ময় বিমূঢ় স্বরে বললো, কাল তোমার বিয়ে আর আজ হঠাৎ এখানে চলে আসার মানে ? নাহার নির্বিকার গলায় বললো, বিয়ে আমার হয়ে গেছে। কার সাথে ? কাসেদ চমকে উঠল যেন। ক্ষণকাল ওর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নাহার। তারপর অত্যন্ত সহজ কন্ঠে বললো, যার সাথে হয়েছে তার কাছেই তো এসেছি আমি। তাড়িয়ে দেন তো চলে যাই। কাসেদ বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো ওর হলুদ মাখানো মুখের দিকে। কিছুতেই সে ভেবে পেল না, সেই চাপা মেয়েটা আজ হঠাৎ এমন মুখরা হয়ে উঠলো কেমন করে।৪০
‘এটা সমাজেরই রূপ. এমন পানি গড়াতে গড়াতে নিচে বেয়ে স্থির হয়। মাৎসন্ন্যায়ের সমাজে এমনই হবে। কাসেদের মত স্বল্প আয়ের টানাটানির কেরানীদের, তাকে বিয়ে করতে হলো নাহারকে, যাকে নিয়ে কখনো কল্পনার আকাশ নির্মাণ করেনি।’৪১ এভাবেই জহির রায়হান উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে কাহিনীর প্রয়োজনে বিধৃত করেছেন। গল্পের প্রয়োজনে যতটুকু দরকার ঠিক ততটুকুই বর্ধিত করেছেন চরিত্রগুলোকে। এতে হয়তো কোন কোন চরিত্রের বিকাশ হয়নি, বিন্দু বিন্দু ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে চরিত্রগুলি ভাসা ভাসা ভাবে এসেছে তবুও সমাজ গৃহের একটি সাম্যক ধারণা রয়েছে উক্ত চরিত্র চিত্রণের মধ্যে যা একজন সার্থক শিল্পীর কাছে একান্ত কাম্য।
আঙ্গিক বিচার :
সার্থক উপন্যাস নির্মিতির প্রশ্নে বিষয় ও আঙ্গিকের সমন্বিত রূপায়ণ অনিবার্য। শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসটি জহির রায়হানের প্রথম উপন্যাস হলেও ঔপন্যাসিক এখানে জীবনের অতি বাস্তব ঘটনাকে রূপায়িত করেছে সাবলীল বাণীব্যঞ্জনায়। বিষয়ের সাথে মিল রাখতে চেয়েছেন আঙ্গিকের। বর্ণনাভঙ্গির ক্ষেত্রে তিনি কিছুটা চৈতন্যপ্রবাহ রীতিকে অনুসরণ করেছেন। ব্যক্তি চরিত্রের মনোবিশ্লেষণের অন্যতম একটি রীতি চৈতন্যপ্রবাহ রীতি। এ রীতিতে লেখক কর্তৃক উপন্যাসের কাহিনী,ঘটনা ও দৃশ্য বর্ণনায় প্রচলিত রীতির জায়গায় বর্ণনাকারী হিসেবে আসে কোনো ব্যক্তি চরিত্র। চেতনাপ্রবাহ রীতির উপন্যাসের ধারা প্রধানত দুটি।
(১) অন্ত বিশ্লেষণ (Internal analysis) রীতিকে চরিত্রের বাইরে থেকেও লেখক চরিত্রে অন্তর্জগৎ দেখেন এবং প্রতিটি মুহূর্তকে ধরার চেষ্টা করেন।
(২) অনুচ্চার মনোকথন (Interior monologue) রীতিতে বর্ণনার রীতি ও দৃষ্টিকোণ চরিত্রের চেতনার উপর নির্ভরশীল।
বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে গোপাল হকালদার তাঁর ত্রিবিদা উপন্যাসে প্রথম এ রীতি ব্যবহার করেন। বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত বাংলা উপন্যাসে চৈতন্যপ্রবাহধর্মী লেখকদের পুর্বসূরি। পরে কমল কুমার মজুমদারের উপন্যাসে তার বিশেষ অভিব্যক্তি লক্ষ করা যায়। আর বাংলাদেশের উপন্যাসের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহই প্রথম লেখক যিনি চৈতন্যপ্রবাহকে প্রথম উপন্যাসে ব্যবহার করলেন। শেষ বিকেলের মেয়ে তে জহির রায়হান অনেকটা অচেতন ভাবেই এ রীতি অনুসরণ করেছেন। এ রীতির প্রথম বৈশিষ্ট্য অন্তর্বিশ্লেষণ উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায়। এখানেও লেখক বাইরে থেকে কাসেদের মধ্যে দিয়ে তাঁর অন্তর্জগৎকে ধরতে চেয়েছেন। কাসেদ প্রায় কল্পনায় মগ্ন হয়ে যেত, জাগর স্বপ্ন দেখত এবং তার মানস জগতের দুরধিগম্য ও গভীরতর প্রদেশের ভাবনাবলি ব্যক্ত হয়ে যেত। বর্ণিত আছে-
পা থেকে মাথা পযর্ন্ত জাহানারাকে দেখে নিলো কাসেদ। আজ ওকে আগের চেয়ে অনেক বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক আকর্ষণীয়। ওর চোখের আর মুখের লাবণ্য অনেক বেড়ে গেছে। কথার মধ্যেও আশ্চর্য পরিবর্তন। কাসেদের মনে হলো সে যেন এ মুহূর্তে আরো বেশি করে ভালবেসে ফেলেছে ওকে। তাকে পাবার আকাক্সক্ষা আরো তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে ওর মনে। না, জাহানারাকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যতের কোন কিছুই কল্পনা করতে পারে না কাসেদ। কিছুই না ।৪২
কেন্দ্রীয় চরিত্র এমন বিভোল মনে মগ্ন থাকলেও লেখক বারবার বর্ণনার মধ্যে ঢুকে পড়েছেন যাতে এ রীতির পূর্ণবিকাশ সম্ভব হয় নি।
অন্যদিকে অনুচ্চার মনোকথন রীতিরও সন্নিবেশ ঘটেছে এখানে। কাসেদ ভালবাসে জাহানারাকে। তবে জাহানারা তাকে ভালবাসে কিনা তা জানার প্রয়োজন মনে করেনা কাসেদ। বরং নিজের চেতনার উপর নির্ভরশীল হয়েই ভবিষ্যৎ কল্পনা করে। ফলে বার বার ভুল করে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তাইতে জাহানারা তাকে বলে-
‘জাহানারা পরক্ষণে বললো, কাউকে ভালবাসতে যাওয়ার আগে তার সব কিছু জেনে নেয়া উচিত, নইলে পরের দিকে অশেষ অনুতাপে ভুগতে হয়।’৪৩ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর চাঁদের অমাবস্যা উপন্যাসের আরেফ আলীর সঙ্গে কাসেদের মিল রয়েছে। রাতের আবছায়াতে একটি হত্যাকা- দেখার পর আরেফ আলীর স্বাভাবিক জীবনের শান্তিবিনষ্ট হয়েছে। জাগতিক কাজগুলো প্রথা মাফিক করলেও তার অন্তরে বয়ে চলে চেতনার সূক্ষ্মস্রোত। এ উপন্যাসের কাসেদ জাহানারাকে ভালবেসে তার চেতনায় মগ্ন হয়েছে। ফলে অফিসে কাজ করতে মন বসেনা। আনমনে সাদা কাগজে জাহানারার নাম লিখে পূর্ণ করে। আবার তা কালি দিয়ে ঢেকে দেয়। জাহানারাকে নিয়ে নানা প্রকার হ্যালুসিনেশনে ভুগতে থাকে। কাসেদের এই যন্ত্রণা পিড়িত আত্মঅনুসন্ধান ও আত্মআবিষ্কার সবই চেতনাপ্রবাহ রীতিতে অগ্রসর হয়েছে। তবে চৈতন্যপ্রবাহ রীতির উপন্যাসে যে আপাত-অসংলগ্নতা থাকে তা এ উপন্যাসে নাই। শুধুমাত্র মকবুলের মেয়ে পরিচয় দিতে অস্পষ্ট ও ধোঁয়াটে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন। উপন্যাসে তার নামটি পর্যন্ত নেই। তাকে এক বার সন্ধ্যায় আবছা- আবছা দেখেছিল কাসেদ। ঘটনা ক্রমে কাসেদের জীবনে সেই মেয়েটি সন্ধ্যার মতো আবছাই রয়ে গেল। এভাবে উপন্যাসটিতে উভয় রীতির আংশিক বৈশিষ্ট্য প্রযুক্ত হয়েছে।
ভাষা রীতির ক্ষেত্রে জহির রায়হান চরিত্র ও বিষয় অনুসারে ভাষা ব্যবহার করে নৈপুণ্য ও শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ উপন্যাসের ভাষা মানবাংলার গ্রামীণ চরিত্র না থাকায় আঞ্চলিক ভাষার সংযোজন অনুপস্থিত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাক্যের সহজ সাবলীল বর্ণনাও তাঁর উপন্যাসকে অনন্য মাত্রা দিয়েছে। উপন্যাসের বর্ণনাভঙ্গি সংলাপধর্মী, ভাষার মাধূর্য কারুশিল্পের মত স্পষ্ট। বর্ণিত আছে, ‘কাসেদ বললো, লড়াই শুধু রাজার সঙ্গে রাজার, এক জাতের সঙ্গে অন্য জাতের আর এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশেরই হয় না। একটি মনের সঙ্গে অন্য একটি মনেরও লড়াই হয়।’৪৪ অন্যত্র বলেছে- ‘সে মন ও আমার। আমার নিজের। একজন চায় স্বার্থপরের মত শুধু পেতে । অন্যজন পেতে জানে না,জানে শুধু দিতে। বিলিয়ে দেয়ার মধ্যেই তার আনন্দ।’৪৫
এছাড়া ঔপন্যাসিক কাহিনির রূপনির্মাণে ও ঘটনার পারম্পর্য বোঝাতে প্রচুর উপমা, অলংকার ও চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। তাঁর অধিকাংশ সৃষ্টিকর্মের মতো এ উপন্যাসের শুরুতে প্রকৃতি নির্ভর চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন। যেমন-‘আকাশের রঙ বুঝি বার বার দলায়। কখনো নীল। কখনো হলুদ। কখনো আবার টকটকে লাল।’৪৬
বিকেলের রোদকে একটি মেয়ে দেহের সঙ্গে তুলনা করে উপমা ব্যবহার করেছেন বেশ কয়েকটি জায়গায়। যথা-
* ‘সেই মেয়েটিকে দেখবে। বিকেলের রঙে যার দেহ রাঙানো। ’৪৭
* ‘দাঁতগুলো চিকচিক করছে বিকেলের রোদ।’ ৪৮
* ‘লাল সূর্যটা হারিয়ে গেছে উচু উচু দালানের ওপাশে।’৪৯
* ‘শেষ বিকেরের সোনালি আভায় মসৃণ পাখাটি চিকচিক করছে তার।’৫০
এছাড়া তাঁর বর্ণনাভঙ্গি কাব্যময় ও হৃদয়গ্রাহী, যেন কোমল-স্নিগ্ধ ঝর্ণাধারার মত প্রবাহিত হয়েছে অনন্তের পানে। যেমন-
‘পাশের বাড়ির ছাদে মেলে দেয়া কুমারী মেয়ের হাল্কা নীল শাড়িখানা বাতাসে পতাকার মতো উড়ছে পতপত করে।’৫১
তাছাড়া তাঁর এ রচনায় প্রচুর লোকসংস্কার, লোকবিশ্বাস ও প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহার করেছেন। এসব অলঙ্কার সংযোজনের মাধ্যমে কাহিনী ও বিষয়কে নিপুণভাবে পরিস্ফুটিত করে তুলেছেন। লোকসংস্কারগুলি এমন- ‘মেয়েদের বয়স জিজ্ঞাসা করতে নাই।’
প্রবাদ প্রবচনের মধ্যে রয়েছে ‘ধোপার গাধা আর কোম্পানির অফিসের কেরানির মধ্যে পার্থক্য নেই।’ অথবা ‘চাওয়া পাওয়ার সঙ্গে সাপে নেউলের সম্পর্ক রয়েছে।’
এ উপন্যাসের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য লেখকের দার্শনিক উক্তি। তিনি উপন্যাসের গতির ব্যবহৃত করে নয়, বরং বর্ণনা ও ঘটনার সঙ্গে মিল রেখে তাঁরা নিজস্ব দর্শন ফুটিয়ে তুলেছেন। যেমন-
* ‘যে গাছে প্রাণ নেই তার গোড়ায় পানি ঢেলে কী হবে।’৫২
* ‘দুই দেহ, একমন। মেয়েজাতটাই বোধ হয় এমনি।’৫৩
* ‘মেয়েরা এমনি হয়। তারা যাকে ভালোবাসে তাকে বড় স্বার্থপরের মত ভালবাসে।’৫৪
‘জাহানারার প্রতি কাসেদের একমুখী প্রেমও তার প্রত্যাখান জনিত কারণে ঈর্ষামূলক প্রতিক্রিয়ায় শিউলির কাছে আত্মনিবেদন এই হচ্ছে শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসের কাহিনী। সাধারণ এই উপকরণকে জহির রায়হান তাঁর জীবনবোধের মৌল আবেগের সঙ্গে অনেকাংশে সমন্বিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।’৫৫ এছাড়া শিল্পরূপ বিশ্লেষণে ‘সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিন্যাসকে বুঝতে সাহিত্য যদি কিছু সাহায্য করে তাহলে লোকজীবন, লোককথা, মিথ...ইত্যাদির সঙ্গে...মানুষের অর্থনৈতিক এবং উৎপাদনশীল জীবনে এসবের প্রাধান্য ব্যাপক।’৫৬ এ ক্ষেত্রে শেষ বিকেলের মেয়ের শিল্পরূপের সফলতা রয়েছে। অনেক গবেষক একে গবেষণায় স্থান দেননি কিংবা উপন্যাস বলতে নারাজ। কেউ কেউ মনে করেন, ‘জহির রায়হানের শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাস নয়, বড় গল্প।’৫৭
মূলত শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসে জহির রায়হান তাঁর রোমান্টিক মনের মাধুরী মিশিয়ে জীবনের রং ধরতে চেয়েছেন, উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের স্বপ্ন , কল্পনা, আশা-আকাক্সক্ষার বাসর নির্মাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, রাজনৈতিক সচেতন শিল্প কাহিনীর উপযোগী করে অতি অল্প কথায় রাজনীতিকেও অনুষঙ্গ করেছে। জীবনে সমুদ্রের বালুচরে ঘুরে ঘুরে তিনি নুড়ি কুড়িয়েছেন এবং তা দিয়ে প্রাসাদ গড়তে সচেষ্ট হয়েছেন। হয়তো কোথাও ক্ষয়ে গেছে, হয়তো কোথাও সৌন্দর্যহানী ঘটেছে,তবু নিদৃষ্ট অবয়বে সমাজ কাঠামোর বাস্তব চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছেন এ উপন্যাসে । এ উপন্যাসে তিনি ঘটনার ঘনঘটাকে স্থান দেননি, বরং কাসেদের বাড়ি,অফিস,মকবুল সাহেবের বাড়ি এবং রিক্সা চড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। চরিত্রগুলিকেও বিস্তৃত করেননি, এতে হয়তো শিউলি, জাহানারা কিংবা সালমার বৈশিষ্ট্য গভীরভাবে উন্মোচিত হয়নি তবু তাদের সামগ্রিক ধারণা উপন্যাসে বর্তমান। তিনি হয়তো চেয়েছেন কাসেদের চরিত্রকে আবর্তন করতে। এ কারণেই অন্যান্য চরিত্রর প্রাধান্য কম। কাসেদকে এমনভাবে গড়েছেন যার মধ্যে সরলতা আছে কিন্তু, শঠতা নাই। তার আত্ম সম্মান আছে, হৃদয় আছে, আছে মানবিকতা বোধ, অফিসের পরচর্চায় সে কান দেয় নি। কাউকে অসম্মান করেনি বা হিংসা করেনি। মকবুল সাহেবের অসুস্থতা ও অসহায়ত্বে সহানুভূতি জানায়, বড় সাহেবের অশান্তিতে তারও চিন্তা হয়। সালমার বিপদকে দূর করতে চায়, শিউলির চপল মন বোঝার চেষ্টা করে, মায়ের উদ্বিগ্নতা তাকেও পীড়া দেয়। তবে তার চরিত্রে কিছুটা দুবর্লতা আছে। সে সক্রিয় নয়, নায়কের মত সংগ্রামীও নয়। সুযোগ থাকলেও পেশা পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করে নি। কল্পনা করেছে বেশি। কিন্তু তা প্রয়োগে সচেষ্ট হয় নি। তাইতো বারবার অন্যের কাছে পরাজিত হয়েছে, ঔপন্যাসিকও একাধিক বার তার উল্লেখ ঘটিয়েছেন। নিম্ন মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হয়েও তার মধ্যে সংগ্রামী মানসিকতা অনুপস্থিত এসব দিক থেকে চরিত্রটি কিছুটা ত্রুটিপূর্ণ হলেও জহির রায়হান তাঁর হৃদয়ের কোমল পরশ দিয়ে কাসেদ চরিত্রটি নির্মাণ করেছেন। মূলত ও উপন্যাসে জহির রায়হান অতিসাধারণ মানুষের অন্তরের গহীনে লালিত স্বপ্নকে নিখুত,মননময় ও যথার্থ গড়নে আঁকতে সক্ষম হয়েছেন। জীবনের গভীর বিশ্লেষণ, অতলান্ত উপলদ্ধি স্বপ্ন ভেঙ্গে যাওয়ার নিদারুণ মর্মঘাতী রূপ তথা জীবনে নানা রঙ্গের ছবি এঁকেছেন। শুধু তাই নয়, স্বপ্নময় রঙ্গিন জীবনের অধিকারী শুধু ধণিক শ্রেণি, অর্থনৈতিকভাবে বিড়ম্বিত অস্বচ্ছলদের ভাগ্যে তা জোটে না, তার উপর সুবিধাবাদীরা দুশ্চিন্তার আঁধার মাখিয়ে দেয়- এমন বাস্তব সত্যকেও তিনি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়েছেন।
উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, শেষ বিকেলের মেয়ে উপন্যাসে জহির রায়হান বিষয়বস্তুর সঙ্গে প্রকরণরীতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর প্রাঞ্জল ও সাবলীল ভাষা বিন্যাস উপন্যাসে নতুন মাত্রা দান করেছে। দীর্ঘ বর্ণনা নেই বরং সুকৌশলি দক্ষ হাতে পরিচ্ছন্ন ও ক্ষুদ্র সংলাপ রচনা করেছেন। লোকজ শব্দ ও সংস্কারকে অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। সহজ সাধারণ কথোপকথনের মধ্য দিয়ে ঘটনার প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে তাঁর নিজস্ব মতাদর্শ ব্যক্ত করেছেন। মোটকথা, বলা যায় সুনিপুণ শিল্প অবয়ব না হলেও জহির রায়হানের উপন্যাসের প্রথম প্রচেষ্টা হিসেবে শেষ বিকেলের মেয়ে যথেষ্ট সার্থকতার দাবিদার।
তথ্যসূত্র :
১. সারোয়ার জাহান, জহির রায়হান , বাংলা একাডেমি, ঢাকা ১৯৮৮ পৃ-৯
২. বিস্তৃত পাঠের জন্য দ্রষ্টব্য (ক) Sir Jadunath Sarkar (edited), History of Bangal, Voll.11.1945.Dhaka, Dhaka University, P-270 (খ) Abdul Karim. Dhaka. The Mughal Capital. 1964. Dhaka. Asiatic Society of Pakistan. p-1-2
৩. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪/ জুন ১৯৯৭, প্রথম পুনমুদ্রণ-ফাল্গুন ১৪১৫/ ফেব্রুয়ারি ২০০৯, পৃ-১১৫
৪. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬০
৫. মাহমুদুল বাসার, জীবনশিল্পী জহির রায়হান, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাবাজার, ঢাকা, বইমেলা ২০১১, ফাল্গুন ১৪১৭, পৃ-৩৩-৩৪
৬. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), আহমদ পাবলিশিং হাউস, বাংলাবাজার, ঢাকা, জানুয়ারি ২০১২/ মাঘ ১৪১৪, পৃ ৭৭-৭৮
৭. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-২৪-২৫
৮. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৪১
৯. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৫৯
১০. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬০
১১. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪
১২. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬৩
১৩. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৮০
১৪. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৪০
১৫. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-২২
১৬. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬১
১৭. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৪৪
১৮. বদরুল হাসান, উনিশ শতক: নবজাগরণ ও বাঙলা উপন্যাস, জগৎমাতা পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ-১
১৯. জলফিকার মতিন, লক্ষ্যসেথা স্থির, স্বদেশ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ-১৭
২০. রফিকুলউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, পৃ-৩৭৫
২১. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-২৫
২২. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬৭
২৩. রফিকুলউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, পৃ-১৬০
২৪. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-১৫
২৫. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬২
২৬. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৮০
২৭. রফিকুলউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ- ১০
২৮. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-১৫
২৯. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-১৩
৩০. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৩০
৩১. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬৭
৩২. মাহমুদুল বাসার, জীবনশিল্পী জহির রায়হান, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৫
৩৩. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৭৭
৩৪. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৭৩
৩৫. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৮০
৩৬. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮
৩৭. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৩৪
৩৮. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৩৭
৩৯. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-১৬
৪০. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-১৬
৪১. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪
৪২. মাহমুদুল বাসার, জীবনশিল্পী জহির রায়হান, প্রাগুক্ত, পৃ-৩৯
৪৩. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬৫
৪৪. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৭১
৪৫. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৭৮
৪৬. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৭৯
৪৭. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-১৩
৪৮. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৫৬
৪৯. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৬৪
৫০. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৮৩
৫১. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪
৫২. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৮৪
৫৩. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৫৮
৫৪. জহির রায়হান রচনাবলী (১ম খ-), প্রাগুক্ত, পৃ-৪৬
৫৫. রফিকউল্লাহ খান, বাংলাদেশের উপন্যাস বিষয় ও শিল্পরূপ, প্রাগুক্ত, পৃ-১৬০
৫৬. তুষার প-িত: অভিজিৎ সেনের একটি উপন্যাসের নিবিড় পাঠ; দিবারাত্রির কাব্য পত্রিকা, কলকাতা, জুন ১৯৯৯, পৃ-১৩৮
৫৭. মনসুর মুসা: পূর্ব বাঙলার উপন্যাস, পূর্বলেখ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ-৯০।
*প্রভাষক বাংলা,
উইল্স লিট্ল ফ্লাওয়ার স্কুল এন্ড কলেজ।
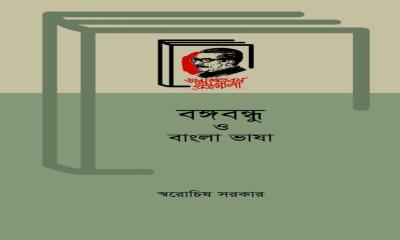












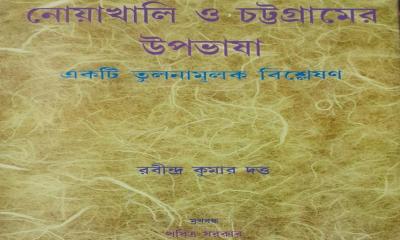





আপনার মতামত লিখুন :