
চন্দন আনোয়ার (জন্ম ১৯৭৮) বাংলাদেশের এই সময়ের প্রতিশ্রুতিশীল কথাসাহিত্যিকদের অন্যতম একজন। তিনি অসংখ্য গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখছেন। তাঁর প্রকাশিত গল্পগ্রন্থের সংখ্যা পাঁচটি :১. প্রথম পাপ দ্বিতীয় জীবন, ২. অসংখ্য চিৎকার, ৩. পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কণ্ঠস্বর, ৪. ত্রিপাদ ঈশ্বরের জিভ, ৫. ইচ্ছামৃত্যুর ইশতেহার। এই পাঁচটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অর্ধ-শতাধিক গল্পের মধ্য থেকে নির্বাচিত তিরিশটি গল্প নিয়ে কলকাতার একুশ শতক প্রকাশনী থেকে পশ্চিমবাংলার প্রখ্যাত কথাশিল্পী সাধন চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘ মূল্যায়নসহ ‘নির্বাচিত ৩০’ শিরোনামে একটি গল্পের সংকলন বেরিয়েছে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে। এই সংকলনের তিরিশটি গল্পই আলোচ্য প্রবন্ধের বিষয়। প্রচণ্ড অন্তর্দাহর সাক্ষী চন্দন আনোয়ারের তিরিশটি ছোটগল্প! কেবল পরিমাপেই ছোট। অভিঘাত মারাত্মক। পাঠককে ভাবতে বাধ্য করেÍচোখের জলে, শিরদাঁড়ার ঠান্ডা স্রোতে, গায়ে কাঁটা দেওয়া অনুভূতিতে। সাধন চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছেন, ‘চন্দন আনোয়ার প্রায় সকল গল্পের শুরু থেকেই আখ্যানে চাপা একটি টেনশন তৈরি করে। কাহিনির কোন ঘনঘটা থাকে না। পাঠক টেনশনের সুতো ধরে ক্রমশ কৌতূহলকে মেলতে মেলতে শরীরের সম্প্রসারিত অংশ নিয়ে ক্রমশ দেশ হয়ে ওঠে।’
আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের একটিমাত্র কথাতেই এই তিরিশটি গল্পের মূলে নিহিত যন্ত্রণাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে দেওয়া সম্ভবÍ“১৯৭১ সালের মতো স্বাধীন আমরা কোনদিন হইনি, হতে পারবো বলেও মনে হয় না। “লেখকের নিজের ভাষায়Í“শালার স্বাধীনতারে!” “রাষ্ট্রের তৃণমূল থেকে টপে স্বাধীনতার বিরোধীদেরই ভয়ানক আস্ফালন! স্বাধীনতাটাকেই মানে না।” (কবি ও কাপালিক) “আপনি যে খুন হবেন, আপনি নিজেও জানেন! বিচক্ষণ কবি আপনি .... যদি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্রের চশমা চোখে না পরতেন আর দালালি না করতেন, শেখ সাদী, ওমর খৈয়াম, আল্লামা ইকবালের মতো বড়ো কবি হতে পারতেন! সেই শক্তি আপনার আছে। থাক, সে কথা বলে কী লাভ! আপনার মগজে তো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, মুক্তিযুদ্ধের পানি জমে আছে।” ‘মালাউনের’ হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে পাল্টে ফেলতে হবে জাতীয় সঙ্গীত নচেৎ খুলি ফুঁড়ে বেরিয়ে যাবে গুলি। এমত শর্ত শুনেও যখন ‘কবি ও কাপালিক’ গল্পে সপাটে উঠে দাঁড়িয়ে কবি গাইতে থাকেনÍ“আমার সোনার বাংলা/আমি তোমায় ভালবাসি”Íতখন মনে হয় যথার্থ স্বাধীনতার উৎস সন্ধানে এক রক্তপথ হাতড়ে এগিয়েছেন লেখক। কখনও বিষাদকে চাপা দিয়েছেন শ্লেষে, কখনওবা আত্মবিদ্রূপে হয়েছেন নির্মম। আবার কখনও চূড়ান্ত হতাশা-আচ্ছন্ন মনে প্রশ্ন তুলেছেন এই আত্মঘাতী ইতিহাসের শেষ পৃষ্ঠায় শেষ দাঁড়িটা কে টানবেনÍ“এই ইতিহাস, বাঙালির এই আত্মঘাতী ইতিহাস তুমি জানো না! দেশভাগের হিড়িকে মান-সম্মান নিয়ে বাঁচার জন্যে বাবা তার যুবতী মেয়েকে নাই করে দিয়েছে, ভাই নাই করে দিয়েছে তার যুবতী বোনকে। আবার, মেয়ে নিজেই বাবা-ভাইকে বাঁচার পথ করে দিয়েছে। ঘরের মেয়ে-বউকে একবার ঘর থেকে বের করে নিলে তাকে আর ঘরে তোলা হয়নি। পাশবিক দংশনে ক্ষতবিক্ষত শরীর-মন নিয়ে এরা অন্ধকার জীবন বেছে নিয়েছে। এই হিংসার ইতিহাস তুমি জানো না? এই ঘৃণার ইতিহাস তুমি জানো না! নাকি জেনেও পালিয়ে বেড়াচ্ছো? ...এই ইতিহাসের শেষ হবে কোন প্রজন্মে? বলতে পারবে?” (ইচ্ছামৃত্যু)
‘মা’কে হত্যা করার যে নির্মমতা তা ভীষণভাবে প্রতীকি ‘মা ও ককটেল বালকেরা’ গল্পে। যেটুকু আলগা সুতোর টান ‘আইনা’ কে মানুষের মতো করে তুলতে পারত তাকে এমন নৃশংস পরিণতি কেন দিলেন, চন্দন? নাহয় আইনা ‘ককটেল বালক’ এক, তবু দিনের শেষে মায়ের কাছে পৌঁছানোর আকুতি, তাকে ফিরিয়ে আনলেও আনতে পারত মূলস্রোতে। অকথ্য-অশ্রাব্য ভাষার ব্যবহারও তাঁর ‘মা ও ককটেল বালকেরা’ গল্পে যোগ করেছে এক বিশেষ মাত্রা। অপ্রয়োজনীয় মনে হয়নি কখনই বরং রাষ্ট্র যে বিশেষ উদ্দেশ্যে বস্তিবাসী, নিরক্ষর, রুজিরোজগারহীন, নিঃস্ব যুবকদের ব্যবহার করে তাকে এই গল্প কষায় প্রচণ্ড এক থাপ্পড়! ‘মাইয়া মাইনষের’ কাটা মুন্ড নিয়ে ফুটবল খেলার যে কল্পচিত্র অথবা “বুকের খোলা লালচে জমিনে লাঠির এলোমেলো গুঁতোর লালছাপ(এর) বাংলাদেশের মানচিত্র” হয়ে যাওয়া, সবটাই রাষ্ট্রের নপুংসকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। এ যেন পাঠককে (নাকি রাষ্ট্রকে!) ইলেকট্রিক চেয়ারে বসিয়ে শকথেরাপি! শিরদাঁড়ার ঠান্ডা স্রোতে ভাবতে আপনাকে বাধ্য করবেই।
মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর সময়ে প্রতিবাদের বীজ একটু একটু করে প্রোথিত হচ্ছিল নবীন প্রজন্মের মধ্যে। তৈরী হচ্ছিল শাহবাগের পথ। লেখক নিজেও বুঝি সেই পথেরই প্রদর্শক তাঁর ‘অসংখ্য চিৎকার’ গল্পে। প্রশস্ত একটি পুকুর যখন বীরদর্পে ‘খানসেনাদের’ দ্বারা ব্যবহৃত ও নিহত যুবতীদের লাশ চাপা দিয়ে দিয়ে অপ্রশস্ত করে নিয়ে আসে জমির খাঁয়ের মতো মানুষেরা তখন তারা স্বপ্নেও ভাবে না তুচ্ছ একটি লাল নিশান, নিরীহ, নীরব একটি লাল নিশান কেড়ে নিতে পারে তাদের দিন ও রাতের নিশ্চিন্ত ঘুম। নিñিদ্র একটি ভয়ের আবহে লেখক ধীরে ধীরে তৈরী করেন গূঢ় রহস্যের জাল। পুকুরপাড়ের বটগাছ থেকে গুনে গুনে এগারো পা মেপে পোঁতা হয় সাতটি লাল ধ্বজা। উত্তুরে হাওয়ায় তাদের অহংকারী আস্ফালন বুঝি সদর্পে ঘোষণা করে যথার্থ ও কাঙ্খিত স্বাধীনতা। গোয়েন্দা গল্পের মতো দুইয়ের সঙ্গে দুই যোগে চার প্রমাণ না করেও গল্পের শেষে উন্মোচিত হয় রহস্যের ভয়াবহ আব্রু। শিউরে ওঠে পাঠক। এখানেই নিহিত গল্পের সার্থকতা।
কখনও আবার স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা, আদর্শের অপমৃত্যু বুকে নিয়ে লেখক হয়ে ওঠেন বিদ্রƒপাত্মকÍ“সব ইস্তফা দিয়ে এখন ইনকামের শর্টকাট লাইন। পলিটিক্স। এই লাইনে এক টাকাও পুঁজি লাগে না। লাভ আছে, লোকসান নেই। এক বছরে ভালই কামিয়েছে।” ‘করোটির ছাদে গুলি’ গল্পে এমনভাবেই ‘টাকার গন্ধে ফুসফুসকে গোসল করানোর’ যে অনুষঙ্গ তা মারাত্মকভাবে হয়ে ওঠে বাস্তব। তবু এই কঠিন, নির্মম বাস্তবের মাঝেও কোথাও যেন “চোখে নোনাজলের জাফরি কাটা পর্দা” বা “ডানাকাটা গেঞ্জি” র কাব্যময়তা বিছিয়ে থাকে অনেকক্ষণ।
আবার ‘গিরগিটি ও একটি মেয়ে’ গল্পে স্বাধীনতা-উত্তর দেশের ভবিষ্যত নেতাদের কুৎসিত হিপোক্রিটিক চেহারা বেদনার্ত লেখককে করে তোলে শ্লেষাত্মক“এত দামের নেতা এ-খা-নে!....পাক আর্মির সাথে ওদের পার্থক্য রইল কৈ! ...ওরাই দেশের ভবিষ্যত নেতা! একদিন সংসদ কাঁপাবে। ওদের গাড়িতেই লাল সবুজের পতাকা পতপত করে উড়বে! স্বাধীনতার ঝকমকে সোনালি ফসল ওদের ভোগ দখলে যাবে! অলরেডি পেতে শুরু করেছে! ভবিষ্যত মন্ত্রী-এমপিদের এই কুৎসিত রূপ কোনদিনই মানুষ জানবে না! শকুনের মতো খাবলে খেলো মেয়েটাকে! ওরকম কত মেয়ে ওদের ক্ষুধা চরিতার্থ করতে অন্ধকারে এইভাবে মাটি কামড়ে পড়ে থাকে কে জানে!” লক্ষণীয়, প্রতিটি বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে বিস্ময়সূচক চিহ্ন। বিস্ময় তবু কম পড়ে। ‘মেয়েটা কেমন গুমরে গুমরে কাঁদে! সংগ্রামের বছর তার সই সাজেদা এরকম গুমরে গুমরে কাঁদত। খানসেনারা সাজেদাকে তুলে নিয়ে দুইদিন পরে ফিরিয়ে দিয়ে গেছিল। মেয়েটা কী করে অবিকল সেই রকম গুমরে গুমরে কাঁদে! কোথায় পেল সে এই কান্না! খানসেনারা তো কবেই পালাইছে!” ‘গিরগিটি ও একটি মেয়ে’ গল্পে হাজির বউ যখন মেয়েটির কান্নার কারণ তালাশ করেন তখনও তিনি জানতে পারেননি যে খানসেনারা আসলে কোথাও পালায় না। শুধু বদলে নেয় মুখোশ। আর সেই বদলানো মুখোশের আড়ালে তাদের আসল চেহারা চিহ্নিত করার দায় যেন লেখক তুলে নেন নিজ কাঁধে। বিপন্ন তিনি প্রশ্ন ছুঁড়ে দেনÍ‘দেশটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? মেয়েটা কোথায় দাঁড়াবে?” পাঠকও মনে মনে খুঁজতে শুরু করেন উত্তর। অথবা যখন দেখতে পান মনুরা খালার “বুকের খোলা লালচে জমিনে লাঠির এলোমেলো গুঁতোর লালছাপ বাংলাদেশের মানচিত্র হয়ে গেছে” (মা ও ককটেল বালকেরা)Íতখন দেশ আর দেশের মানুষ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।
দেশের মানুষের আবেগ, অনুভূতি, দুর্দশা, আনন্দও তাই লেখক চন্দন আনোয়ারের দৃষ্টি এড়ায় না। নিপুণ রিংমাস্টারের মতোই তিনি তাঁর চরিত্রদের নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। চরিত্রদের ভাবের আদান প্রদানে নিয়ত প্রতিফলিত হয় তাঁর ভাবনা, বোধ ও নিখুঁত পর্যবেক্ষন। আর পাঠক অবাক দর্শকের ভূমিকায় প্রত্যক্ষ করেন সেই কড়চা। “হঠাৎ একটি খালি রিকশা টুংটাং বেল বাজিয়ে অধ্যাপক জামিলের সামনে দাঁড়াল। আসি ভাই, ছেলেটা মর্গে আছেÍবলে লাফিয়ে রিকশায় উঠে বসলেন। বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে রিকশা চালাতে অসুবিধা হওয়ায় চালকের মুখ ঠেলে বেরিয়ে আসলÍআপনার পোলারে কারা খুন করছে?” সেই মুহূর্তে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ান পাঠকও। তবে কী একমাত্র পুত্রের মৃত্যু মেনে নেওয়া এতই সহজ! নাকি ছেলের মৃত্যুর সংবাদে স্ত্রীর ‘সুতোছেঁড়া ঘুড়ির মতো দুমড়ে মুচড়ে’ লুটিয়ে পড়া স্থবির করে দিল অধ্যাপক জামিলের বোধ! গভীর অনুসন্ধানে প্রকাশিত হয় এক অসহায় পিতার কাঁদতে-না-পারার যন্ত্রণা, এক কর্তব্যপরায়ণ স্বামীর অভিভাবকত্বের দায়Í“সিঁড়ি ভাঙতে গিয়ে পা ফসকে দুবার করে পড়ে যেতে গিয়েও শরীরের টাল সামলে পৌঁছে গেলেন গেট পর্যন্ত। গেটের তালা খোলা, তালা লাগানো, চাবি প্যান্টের বাম পকেটে রাখা, এই তিনটি কঠিন কাজ ঠি কঠাক করতে পারায় নিজের ভিতরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেল।” কিন্তু শেষরক্ষা হল নাÍ“লাশবাহী ট্রলির সাথে মৃদু ধাক্কা খেয়ে হেলতে গিয়ে আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারলেন না। ভিতর থেকে রিং ছেঁড়ার পট্ পট্ শব্দ শুনতে পেলেন।” অরাজক দেশের মত্ত প্রশাসনের অবিবেচক পদক্ষেপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল একটি সম্ভাবনাময় ভবিষ্যত, দেশের প্রতি দায়বদ্ধ একটি নিষ্পাপ পরিবার। (মৃত্যু অথবা ঘুম)।
আবার ‘রুগণতার গলি-ঘুপসি’ গল্পে পাঠক মুখোমুখি এমন একজন অন্তেবাসী মানুষের যিনি মানসিক সুস্থতা এবং অসুস্থতার সুক্ষ্ম কাঁটাতার ডিঙিয়ে যেতে পারেন অক্লেশেইÍ “খুব শখ ছিল, বড়ো হয়ে পুলিশ হব। পুলিশ হলে মানুষ পিটানোর লাইসেন্স মেলে।” (বিদ্রƒপ নয়!) যিনি দাঙ্গা-ফাসাদ দেখলেই মাথা গলাতে ভালোবাসেন। যিনি স্বপ্ন দেখেন রাস্তার মাঝখানে দিগম্বর হয়ে দাঁড়িয়ে সাগর কলার আবরণ উন্মোচন করে সেটা খাওয়ার সুখ নেবেন অথবা মাথায় ব্যান্ডেজ জড়িয়ে হাসপাতালের বেডে বসে কমলালেবু খাবেন। এই আপাত-অর্থহীন সাধ সত্যিই অর্থহীন কী! নাকি প্রতীকি? তাঁর মনের নিয়মহীনতার স্পর্ধার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারা সহজ কথা নয় বুঝতে পেরে তাঁর স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যান নিজের বোনজামাইয়ের বাড়ি। স্ত্রী একদিন ফিরে আসবেন এই বিশ্বাসে তিনি বলে ওঠেনÍ‘সেই যে ক্ষিপ্রবেগে ঘর ছেড়ে গেল, সপ্তাহ ঘুরে মাস ঘুরে শেষে বছর ঘুরে এল বউ আর ফিরল না। বড়ো চোটে বড়ো অভিমান। তাই অপেক্ষায় আছি অভিমান কবে ভাঙবে।” অভিমান যে আর ভাঙবে না বুঝতে পেরে বউ কে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে তিনি মুখোমুখি হন এক অমোঘ সত্যেরÍনারী-পুরুষের মধ্যের সেই চিরকালীন দুর্নিবার আকর্ষণÍযা ‘সোসাইটির’ চোখের আড়াল রেখে সংঘটিত হয় এবং যে টান তার বউকে বোনজামাইয়ের কাছ থেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম হয় না। হাসপাতালের বিছানায় শুয়েও ডাক্তার ও নার্সের পারস্পরিক সম্পর্কের রসায়নে তিনি সামনাসামনি সেই একই সত্যের। আবার গভীর রাতের অন্ধকারে শরীরের বেসাতি নিয়ে অপেক্ষারত রমণীর চোখেও পরিলক্ষিত হয় সেই ক্ষিদে। কিন্তু যে প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিতে সবাই অস্বীকৃত তাকেই স্বীকৃতি দিতে পাগলের কোন ভণিতা নেই। এভাবেই লেখক ‘হিপোক্রিটিক সোসাইটির’ মুখোশ উন্মোচনের খেলায় মাতেন। গল্পের শেষে যেখানে পাগলের রক্তঝরা ক্ষতে বেশ্যার নোংরা কাপড়ের যত্নের প্রলেপ পড়ে সেখানে এসে লেখকের রুক্ষ, নির্মম শব্দচয়নের আড়ালেও ধরা দেয় গভীর মমত্ববোধ। বাংলা ভাষার রচনা হলেও লেখক প্রায় প্রতিটি গল্পেই ব্যবহার করেছেন বেশ কিছু ইংরাজি শব্দ। এই গল্পে তারা বিশেষ এক মাত্রা যোগ করেÍ“যায় যায় করে তেত্রিশ বছর চলে গেল লাইফ থেকে।” বা “থার্ড পারসন নিয়ে টানাটানি করিস না..., ক্লিয়ারকাট বলে দিচ্ছি কিন্তু “কিংবা ‘সোসাইটি। সোসাইটি কাকে নিয়ে রে!” “যাই যাব করে শেষে চলেই গেলাম স্পটে। গোলমালের স্পিরিট খুব একটা সুবিধাজনক বলে মনে হচ্ছে না।” “আমি তো ওভার প্রস্তুত। মারামারিতে সাইজ ম্যাটার না ...টেকনিকটাই এখানে মেইন ফ্যাক্টর। ...সেকেন্ড টার্গেট চোখ। থার্ড টার্গেট নাক।” এই শব্দগুলির সৌজন্যে খুব স্পষ্টভাবে চোখের সামনে ফুটে উঠছে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষের অবয়ব। চরিত্রায়নের প্রয়োজনে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি পাঠকের মনে তৈরি করে অদ্ভুত এক অভিঘাত।
“গ্রামের প্রান্তসীমানার মাঠসংলগ্ন বাড়ির ছালামতের মেয়ে শাহিদা বায়না ধরেছে, মাগে, হামি মেলায় যাবো।” কিন্তু ততক্ষণে “অন্ধকার দ্রৌপদীর শাড়ির মতো পেঁচিয়ে ধরছে আকাশের দিগম্বর শরীর।” “মুহূর্তে সাঁই সাঁই শব্দ তোলে কালো ঝড় উঠে আসছে লোকালয়ে।” শাহিদা ছোট্ট বালিকা এক, সবে কুসুমিত হচ্ছে তার শরীর, মনে যদিও এখনও দুরন্ত মেয়েবেলা। সারাদিন হি হি করে পাড়াময় দাপিয়ে ফেরে সে। কিন্তু যতই হোক, মেয়েমানুষ তো, তার দিলখোলা হাসি সমাজের চোখে লাগে। যে অশিক্ষিত সমাজ আট থেকে আশি পর্যন্ত সমস্ত শিশু, বালিকা, মহিলা ও প্রৌঢ়াকে এককথায় ‘মেয়েমানুষ’ বলে চেনে তার পক্ষে এমন ‘উড়নচণ্ডীপনা’ মেনে নেওয়া কী সম্ভব! “শাহিদা বলে, মাগে, হামার গাটা কি আম গাছ হইয়া গ্যালো নাকি! ...তুই দ্যাখ, হামার বুকে আমের গুটি হইয়্যাছে। ...এরপর হতে মেয়ে খালি হিহি করে হাসে। বাঁধভাঙা সেই হাসি রমিজা খাতুনের ভিতরে বারুদের মতো দাউ দাউ করে জ্বলে।” অতএব, অপ্রস্তুত জমিতে লাঙল চালানোর জন্য যুতে দেওয়া হয় ‘কালো ভইষের মতো এক তাগড়া পালোয়ান’। তার অনাবিল, নিষ্পাপ হি হি হাসিতে লাগাম পরাবে সে। চন্দন বড়ই অনুভূতিপ্রবণভাবে শাহিদার কষ্টের বর্ণনা দেন। পুরুষ হয়েও।” অকস্মাৎ নিস্তেজ রাত কাঁপিয়ে ঘুম থেকে শাহিদা চিৎকার দিয়ে ওঠে, মাগে! হামাক বাঁচা! মাগে হামাকে বাঁচা! ভূইষ! ভূইষ! ভূইষ! ...মাগে হামার প্যাট ফাইটা গেছে! মাগে হামার প্যাট কাট্যা ফেলছে! মাগে হামার প্যাটে ছুরি ঢুকাইছে!” হাল চালাতে অসমর্থ হওয়ায় শাহিদাকে সেই ‘কালো ভূইষ’ ফেলে রেখে গেছে বাপের ঘরে। চন্দন বড়ো সাবলীলভাবে রমিজা খাতুনের আশঙ্কা মিশ্রিত যন্ত্রণার বর্ণনা দেন। মা না হয়েও। যখন তিনি বলে বসেনÍ“অবোধ বালিকা জানে না, কতদূর সে এসেছে? কতদূর এলে ফিরে যাওয়া যায় না?”Íসেই অসহায়তার হাহাকার ছড়িয়ে যায় পাঠকের বুকেও। পাঠক স্তব্ধ হয়ে বসে থাকেন খানিক। কোথাও যেন ‘খানসেনা’ আর শাহিদার ‘ভূইষ!’ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।
জীবন, বারবার জীবন দিয়েই প্রমাণ করেছে যে সে সোজা খাতে কখনও বয় না। নাহলে, যে অনন্ত একরাশ বিরক্তি নিয়ে এক সকালে তার দাদুকে মনে মনে শাপান্ত করেছিল দাদি পরলোকগত হতে না হতেই বুড়ো বয়সে আবার বিয়ে করতে যাওয়ার রোখ চেপেছে বলে, সেই অনন্তই যখন গভীর রাতে ‘নতুন দাদির’ হাসির দমকে ভেসে গিয়ে বিরক্ত হয়, ‘নতুন দাদিকে’ বাড়ির কোনও জনমনিষ্যি বরণ করতে এগিয়ে না আসায়, জীবন তখন মুচকি হাসে বৈকি!! দাদুর বিয়ের হাঙ্গামায় যে অনন্ত কলেজে গিয়ে ‘ফ্রেশ কিছু মেয়ে একসঙ্গে দেখে নেবার দুর্লভ সুযোগ’ হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় হাত কামড়েছিল, সেই যখন ‘হাসিকে উপাত্ত করে নির্জন অন্ধকারেই তৈলরঙে আঁকা প্রচ্ছদপটের ছবির মতো নতুন দাদির একটি ছবিও এঁকে ফেলে ভিতরের ক্যানভাসে’ তখন জীবন কিশোরীর মতো বাঁধভাঙা খিলখিল হাসিতে ভাসিয়ে নিয়ে যায় রাতের নিস্তব্ধতা। অনন্তর এখন আর কলেজ থেকে বাড়ি ফিরতে দেরি হয় না। দাদু সম্পর্কে একসময় নির্লিপ্ত অনন্ত এখন দাদুর সেবায় নিবেদিত প্রাণ। রাতের আঁধারে পাশের ঘর থেকে ‘নয়া দাদির’ হাসি ভেসে এলে অনন্ত উদ্বেলিত হয়Í‘রাতে তুমি এতো হাসো কেন? আমার ঘুমের ডিস্টার্ব হয় না?’ জীবনের কাছ থেকেই অনন্ত পাঠ নেয় নারী-পুরুষের চিরন্তন সম্পর্কের সেই রসায়নের। তাই অসমর্থ, অক্ষম দাদুর দাফন-কবরের অনুষ্ঠান না মিটতেই যখন সদ্য বিধবা দাদি উঠোনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ‘ওয়াক’ শব্দের ঝড় তোলে তখন “শরফুদ্দিনকে পেছন থেকে ধাক্কা মেরে জায়গা করে নিয়ে বৃত্তের ভেতরে প্রবেশ” করতেই হয় অনন্তকে।
একই রসায়ন রসে জারিত ‘পিতৃত্ব ও তিনটি চিৎকার’ গল্পের যুবতী আয়ুর্বেদিক ডাক্তার এবং তার কমবয়সী, সরকারি কলেজের অধ্যাপক রোগীর সম্পর্ক “মানুষটা খুব সেয়ানা আদম! সুযোগ পেলেই আদি রসাত্মক কথা শুরু করে। চেয়ারে হেলান দিয়ে মুখ গম্ভীর করে শুনি। কল্পনা করি। ভেতরে তখন পাণিপথের যুদ্ধ চলে।” “এখন সংযমের সব খুঁটি উপড়ে ফেলতে কু-মতলব এঁটেছে মানুষটা। রক্তের অণু-পরমাণুকে উস্কে দিচ্ছে। অদ্ভুত একটা শিহরণে হাঁজর-পাঁজর করি। কেউ যদি ছুঁতো।” অবিবাহিতা যুবতী ডাক্তার তার মন আর রক্তের মধ্যের ঠান্ডা লড়াইয়ে, মনে মনে জিতিয়ে দিতে চায় উত্তাল রক্তস্রোতকেই। কিন্তু সেই রক্তের আস্ফালনের কাছে হার স্বীকার করার পর তার মনে বাসা বাঁধে অপরাধবোধ। সতীচ্ছেদের রক্ত যখন তার শরীরে বীজ বপন করে তাতে প্রাণসঞ্চার করে তখন সে সমাজ-আরোপিত পাপ-পুণ্যের ধ্যান-ধারণার বাইরে বেরিয়ে তার প্রগতিশীল চিন্তা-ভাবনা-শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় না। গল্পের শেষে যখন তার সন্তান তার স্বামীকে ‘আব্বু’ বলে ডেকে ওঠে, এবং তার স্বামীও সুখদ পিতৃত্বের আনন্দে আত্মহারা হয়ে চিৎকার করে ওঠে তখন অজান্তেই তার অন্তরাত্মা কেঁদে ওঠে ‘হায় আল্লা রে!’ মিথ্যের বোঝা সারাজীবন বয়ে বেড়ানো বোধহয় খুব সহজ কাজ নয়!
সেইরকমই আর এক মিথ্যের দায় বহন করে কানু। সে ‘কাফন চোর। ‘শরীরজুড়ে তার মরা মানুষের প্রাচীন গন্ধ। ‘লাশের শরীর থেকে সাদা ধবধবে কাফনের কাপড় চুরি করে হাসেম দফাদার কে বিক্রি করাই তার কাজ। তার বিশ্বাস ‘বেঁচে থাকার ধর্ম পালন করছে সে। এই ধর্মই দুনিয়ার সেরা ধর্ম। ‘রাতের অন্ধকারে তার প্রতিপক্ষ শেয়াল-কুকুর, জ্বিন-ভূত বা ‘শয়তানের ক্যারিকেচার’, কিন্তু মান্যি-গন্যি মানুষের মোকাবিলাও যে তাকে করতে হতে পারে এমনটা বোধহয় সে স্বপ্নেও ভাবেনি। গোরস্থানে উপস্থিত যুবক দুটির কন্ঠস্বরের সঙ্গে পাটের ক্ষেতে অপেক্ষমাণ অধৈর্য শেয়ালগুলোর কর্কশ চিৎকারের মিল পায় সে। লেখক পাঠককে মনে করিয়ে দেন অন্ধকার শুধু কানু একাই দাবি করে না, সমাজের, দেশের মান্যগণ্য লিডার যাঁরা দিনের আলোয় দেশের সম্পদে সিঁধ দেয়, তারাও দাবি করে বৈকি! এই গল্পে লেখক সুনিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন যাদুবাস্তবতার যার ঘোর কেটে বেরোতে অল্প হলেও সময় নেন পাঠক।
সেই একই নিপুণতার সঙ্গে গ্রামের একটি স্বল্প শিক্ষিত তরুণীর সরল বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে লেখক যখন তাঁর “আমি কেউ নই” গল্পে পুঁজিবাদের জটিল তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, তখন তিনি নিঃসন্দেহে হন প্রশংসার দাবিদার। তরুণীটিকে দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে তার স্বামী শফিক আড়তদারের কাছ থেকে বাগিয়ে নিতে থাকে লাখ লাখ টাকার পুঁজি। আড়তদার তরুণীটির সঙ্গলাভের বিনিময়ে তাকে শেখাতে থাকেন পুঁজিবাদের গূঢ় তত্ত্ব। সে এখন কথা বলে আড়তদারের ভাষায়Í‘অভাবের টাটানি শুরু হলে তুমি তো তুমি মা, দেশের সরকার পর্যন্ত হাত পাতে।’ সরকার নাকি আমাদের মাথা দেখিয়ে বিদেশ থেকে টাকা আনে। আমরা প্রত্যেকেই নাকি ঋণী। ‘সেই ঋণের দায় থেকে একটি সদ্যজাতও যেমন মুক্ত নয় তেমনই পুঁজিপতি আড়তদারও কী মুক্ত? দাবার ঘুঁটি হয়ে থাকতে না চেয়ে তরুণীটি যখন পাকাপাকিভাবে ঢাকায় থাকার সিদ্ধান্ত নেয় শফিক সেটা মেনে নিতে পারে না কেন, সেই প্রশ্নও তুলে দেন লেখক। তরুণীটি যখন বলেÍ“নাকি আমার কথা শুনে সেও বুঝতে পেরেছে যে, সে যুদ্ধের মধ্যে আছে”, তখন সেই যুদ্ধ দেশ-কাল-সমাজের বিস্তৃতিকে ছোট করে নিয়ে এসে ব্যক্তিগত সম্পর্কের গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়। আবার তরুণীটির সঙ্গে গলা মিলিয়ে লেখক লিঙ্গ সাম্যের পক্ষেও সওয়াল করেনÍ“প্রয়োজনে ক্ষেত-খামারের কাজ করবেন। লাঙল-গরু-কাস্তে নিয়ে মাঠে যাবেন। জমিতে লাঙল দিবেন। ধান বুনবেন, ধান কাটবেন, বিল থেকে মাথায় করে ধান বাড়ি আনবেন। দুনিয়ার সবখানেই মেয়েমানুষেরা ক্ষেত-খামারে কাজ করে। আপনারাই খালি পারেন না। বারো হাত শাড়ি পরে সারাজীবনের জন্য দাসী হয়ে যান।” এর থেকে সফল এবং সরলভাবে নারীবাদের ধ্বজা ওড়ানো বোধহয় সম্ভব হতো না কোনও গোঁড়া নারীবাদীর পক্ষেও। এই গল্পে লেখক বারবার তরুণীটির ব্যক্তিগত জীবন ও দেশ-সমাজের বৃহত্তর সমস্যার মধ্যে এক অদ্ভুত সমাপতন টেনেছেনÍ‘কোটি টাকা দিতে রাজি সে, শফিক নাকি পাঁচ লাখ টাকা নিয়েই কুপোকাত। পুরুষ মানুষটা টাকা নিতে ভয় পায়! কী করবে এত টাকা দিয়ে, কাজে তো লাগাতে পারবে না। ওকে দোষে কি লাভ। সরকারের ঘরে কত বিদেশী টাকা নাকি মুখথুবড়ে পড়ে থেকে শেষে ফেরত চলে যায়। খরচ করার নাকি হিম্মত নেই।” অথবা “আমাদের গ্রামের সুদখোর মহাজনদের থেকে ওদের পার্থক্য কোথায়?”
তবে, গল্পের শেষে সবথেকে বড়ো প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়ে তিনি জানতে চান জগৎজুড়ে এই পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যের বিস্তারে আমার স্থান কোথায়? “আমি কে?” আমার অবস্থান বা ভূমিকা এই সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তিতে কীভাবে সাহায্য করে? যদি নাই থাকে কোনও ভূমিকা তবে আমি শোষিত হচ্ছি কেন!!
শোষণ বুঝি রাষ্ট্রযন্ত্রের দমননীতির অন্যতম অস্ত্র! যে রাষ্ট্র তার নাগরিকদের দুবেলা ভরপেট খাওয়ার সংস্থান করতে পারে না, যে রাষ্ট্র তার শিশুদের অনাহারে মরতে দেখেও চুপ থাকে, সেই রাষ্ট্রের নপুংসকতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন লেখক তাঁর “পাঁচ শ টাকার নোট” গল্পে। তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর দেশের গভীরতম অসুখের ক্ষত নির্দ্বিধায় উদোম করে দেন পৃথিবীর সামনে, এই আশায় যদি বেআব্রু ক্ষত রাষ্ট্রের লজ্জার সামান্য কাপড়ে আবৃত করা যায়Íখানিকটা ওই তমিজা খাতুনের ছেঁড়া কাপড়ে বুক-পেট-পিঠ ঢাকার ব্যর্থ চেষ্টার মতন। গল্পটি তমিজা খাতুনের শরীর বেচা রোজগারের পাঁচ শ টাকার কড়কড়ে নোটের মতই জেগে থাকবে সময়ের দলিল হিসেবে।
মুক্তিযুদ্ধোত্তর সময়ে সদ্যজাত নবীন রাষ্ট্রকে হাত ধরে দিশা দেখানোর মতো যোগ্য মানুষের অনুপস্থিতিতে শুরু হয় তার দিশাহীন পথচলা। রাজাকার এবং তাদের পা-চাটা স্বার্থান্বেষী মানুষের দল স্বাধীনতার যথার্থ অর্থ উপলব্ধি করতে না পেরে সস্তা গিমিকের পথ বেছে নেয় “ভালো আছি” প্রমাণ করার জন্য। আর রহম আলির মতো স্বাধীনতা সংগ্রামীরা প্রতিদিন রাতের ঘুম ভেঙে জেগে ওঠে স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা বুকে নিয়ে। যে রহম আলির গুলিবিদ্ধ পায়ের শুশ্রƒষা করার শাস্তি হিসেবে তার সহযোদ্ধা যুবতীকে তুলে দেওয়া হয় খানসেনাদের হাতে এবং সারারাত ব্যবহৃত হওয়ার পর তার উলঙ্গ অর্ধমৃত শরীর বাঁশের ডগায় বিদ্ধ করে তিনদিন তিনরাত রেখে দেওয়া হয় রাস্তার তে-মাথায়, সেই রহম আলির সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য ওসি, এসপি বা ডিসি অফিসের তা বড় অফিসারদের যখন ঘাম ও ঘুম দুইই ছুটে যায়, তখন মেকি স্বাধীনতার গলদটা অনাবৃত হয়ে যায় দৃষ্টিকটুভাবে। কোনমতে ডিম বিক্রি করে দিন গুজরান করা রহম আলির বুঝতে অসুবিধা হয় না এই সংবর্ধনার নাটক আসলে তাঁর মেরুদন্ডকেই খরিদ করার জন্য। “পালিয়ে বেড়ায় বিজয়” গল্পের শেষে লেখক তাকে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেন আগুন বুকে নিয়ে। আচ্ছা, এই আগুনকে কী সত্যিই শাহবাগের দাবানলে পরিণত করা যেত না!
রহম আলির মতো মুক্তিযোদ্ধারা ‘ছানা মিঞা’র থেকে দূরে চলে গিয়ে বাঁচার পথ খুঁজলেও, আব্দুর রহিমের মতো কেউ কেউ ‘জমির মৃধা’দের শেষ পর্যন্ত ইঁদুর কলে পেষাই করার জেদ বুকে লুকিয়ে রাখেন। আদ্যন্ত প্রতীকি এই গল্পে আব্দুর রহিম তার বসতবাড়ি বা ধানের গোলা ইঁদুরের হাত থেকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে অবতীর্ণ হয় এক অসম লড়াইয়ে। ইঁদুর তার কান কামড়ে নিয়ে তাকে ক্ষতবিক্ষত করে দিলে, সে ভয় পায় বটেÍ“বউ, এই ইঁদুর তো আমার কান কামড়ে ধরছে। ঘরের দখল নিতে চায়। আরো বড় ইঁদুর আছে! হেদের বড় দল আছে! দেশ দখলের চেষ্টায় তারা!” তবে, তাদের নিধন করার জেদ আরও দৃঢ়বদ্ধ হয় তার। জমির মৃধার কাছে আব্দুর রহিমের প্রশ্ন অনেক আর আব্দুর রহিমের প্রশ্নের কাছে জমা রয়েছে জমির মৃধার আতঙ্ক, অন্যায় করলে যে আতঙ্ক অবচেতনে বাসা বাঁধে, ওই ইঁদুরের গর্তের মতো, তেমন আতঙ্ক। মৃধা যখন সাবিনা খাতুনকে তার কাছে যেতে বলে, মৃধা যখন সাবিনা খাতুনের সাথে তার দাদি অর্থাৎ আব্দুর রহিমের মায়ের সাদৃশ্য খুঁজে পায়Í“সাবিনা খাতুন বড় বড় চোখ করে বাপের দিকে তাকিয়ে বলে, আমি নাকি দাদির লাহান দেখতে অইছি! দাদির লাহান নাকি বুক-সিনা...”, তখন আব্দুর রহিমের আর বুঝতে বাকি থাকে না কেন মায়ের কথা মনে হলেই সে দেখতে পায় জমির মৃধা “শিকার খাওয়া বিড়ালের মতো জিহ্বা চাটে”। আটত্রিশ বছর অপেক্ষার পর আব্দুর রহিম নিজে হাতে তুলে নেয় বিচারের ভার।” আটত্রিশ বছর পরে আসল ইঁদুরটাকে বাগে পেয়েছে সে।”
প্রায় বছর চল্লিশেক আগে পরিত্যক্ত নৃপেন বিশ্বাসের বাড়িতে হঠাৎ একদিন ধূপপোড়ার গন্ধে প্রাণসঞ্চার হলে, জুলমত বয়াতির ‘পাগলামির’ মাত্রা বৃদ্ধি পায়। সে মুক্তিযুদ্ধের আগুন বুকে নিয়ে বাঁচে। ছিয়াত্তর বছর বয়সী রোগা শরীরে তার জ্বলজ্বলে-অভিজ্ঞ দুই চোখ বুঝতে পারে এবারে বিচারের সময় আগতÍসেইসব সুবিধাভোগী, পাক সেনাদের মদতদাতা, মানবিক ধর্ম ভুলে যাওয়া মানুষদের বিচারÍযে আদালতে সেই জজ, সেই উকিল আর সেই সাক্ষী। ‘মৃধা’র গা থেকে বয়াতি যখন মরা মানুষের গন্ধ পায়, সে ভয়ে বিষম খায়। আর ‘মৃধা’ যখন ‘মুন্সি’কে ঘুম থেকে তুলে এই খবর দিতে যায় তখনই চিহ্নিত হয়ে যায় আসামী। জুলমত বয়াতির সেই বিচারের সমর্থনেই যেন তরুণ ছাত্রের দল তাদের যুবক শিক্ষকের সাথে দলবেঁধে গ্রামে আসে মুক্তিফৌজের প্রতীক হয়ে। আর মুহূর্তে চন্দন এঁকে ফেলেন আদ্যন্ত প্রতীকি ও বিমূর্ত এক ছবি তাঁর ‘পোড়োবাড়ি ও মৃত্যুচিহ্নিত কন্ঠস্বর” গল্পে। ‘ছেলেরা ফিরে এসে বলেÍঘটনা সত্যি! এর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন মনে করে না। যদিও জুলমত বয়াতি ওদের থেকে পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়েছিল, তারপরে সেও কন্ঠ শানিয়ে বলে, সত্যি মানে! ডাহা সত্যি! আগুনে পোড়াইলে মানুষ মরেনি? আগুনে পোড়াইলে মানুষ মরে না। মানুষ জ্বিন অইয়া য়া। জ্বিন আগুনের তৈরি না? বিশ্বাসের জ্বিন এই বাড়িডা পাহারা দেয়!” নৃপেন বিশ্বাসের স্কুলে পড়া ছোট মেয়ে, কলেজে পড়া বড় মেয়ে, সুন্দরী বউ এমনকি কাজের মেয়ে হরিদাসীকেও যখন শরীর দিয়ে, জীবন দিয়ে মক্তিযুদ্ধের মূল্য চোকাতে হয়, তখন নৃপেন বিশ্বাসকে তো একা অপেক্ষা করতেই হয় ন্যায়-বিচারের এই দিনটার জন্য। বয়াতির শেখের গান দিয়ে যখন গল্প শেষ হয়, পাঠকও তখন তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইতে থাকেন সেই স্বাধীনতারই গান।
চন্দনের চরিত্রদের গায়ে ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ। বড়ই সাবলীল তাদের চলা-ফেরা, কথা বলার ভঙ্গি। তাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলিও মাটির রসে জারিত। কিন্তু চন্দনের যে রুক্ষ, কঠিন না হয়ে উপায় নেই। যে সময়ের দলিল তিনি লিখে চলেছেন সে যে বড়ই অস্থির এক সময়, যখন ‘সুখ-শান্তির গায়ে শুকনো রক্তের দাগ’ লেগে থাকে। তবু জীবনের পথে নিরন্তর অন্বেষণে ব্যস্ত লেখক। তারই ফলস্বরূপ তিনি লিখতে থাকেন ‘একটি পুকুর মরে যাচ্ছে’, ‘অন্তর্গত শূন্যতা’, ‘বারবনিতা এসোসিয়েশন’ বা ‘অনিরুদ্ধ টানের মতো বিচিত্র স্বাদের গল্প। ‘একটি পুকুর মরে যাচ্ছে’ গল্পে সওদাগর আলি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সর্বোচ্চ এক মিনিট বসলেই বলে দিতে পারেন আগামী। সমস্যার সমাধানসূত্র জানা না থাকলে নিতে পারেন এক নির্মোহ অবস্থান আর ‘গলায় ছুরির দাগ’ আছে বলে করতে পারেন না অন্যায়ের প্রতিবাদ। আবার ‘অন্তর্গত শূন্যতা’ গল্পে পুরুষের শরীরে নারীমন নিয়ে জন্মানো ‘না-মানুষ’ দের প্রতি তথাকথিত শিক্ষিত সমাজের বিরূপতা ভাবায় লেখককেÍ“ঠিক বুঝে পাই না ওদের জন্মাবার কী দরকার ছিল? কী ব্যালেন্স তৈরি করলেন ঈশ্বর? ...ওদের না আছে দেহ, না আছে মন, না আছে আড়াল। ...লাজ-লজ্জা করবে কার জন্য? কেউ কী স্বীকৃতি দিয়েছে? নাকি দেবে কোনদিন?” একইরকমভাবে ‘বারবনিতা এসোসিয়েশন’ গল্পে তিনি সমাজের এই অচ্ছুত মহিলাদের হাতে তুলে দেন শাসনভার। সমাজের ভন্ডামি ও দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে বিদ্রূপের তির শানান লেখক। কিন্তু ‘অনিরুদ্ধ টান’ গল্পটি শেষ হয় নরেন সান্যাল আর জাহের আলি মাস্টারের নির্মল বন্ধুত্বের হাত ধরেÍ“হামাগুড়ি দিয়ে উপুড় হয়ে একমুঠো মাটি হাতে নিয়ে নরেন সান্যাল বলে, এ আমার বাস্তুভিটার মাটি। এই মাটির গন্ধ আমার শরীর থেকে কখনোই যায়নি। ...এদেশে জন্মেছি, এদেশেই মরতে চাই। দেশ কোনদিন পর হয় না ...পারবে না জাহের আমার মুখাগ্নি করতে? তোমার ছেলেরা তো আমারই ছেলে, ওরাই না হয় করবে।”
‘নির্বাচিত ৩০’-এর এই সংকলন একনাগাড়ে বেশিক্ষণ পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না পাঠকের পক্ষে। পড়তে পড়তে ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে মন। সমস্ত সুকোমল বোধ-অনুভূতি ক্রমশ অবশ হয়ে আসে। মনে হতে থাকে রুক্ষতার এই মোড়কে লেখক বুঝি তাঁর পেলব অনুভূতিগুলোকে, তাঁর সুকোমল হৃদয়বৃত্তিগুলোকে পাশ কাটিয়ে যেতে চান। “স্কাইপ ও দুটি মৃত্যুমুখ” গল্পে নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের উপরে ছোট্ট কুকুরছানাটি যখন মানুষেরই মতো অধিকার ফলায় অথবা অভিমান করে না খেয়ে থাকে তখন পাঠক মনে মনে আশ্বস্ত বোধ করেÍ“জজ হাসান সকালের নাস্তার জন্যে কয়েকটি বিস্কুট একটি বাটিতে নিয়ে খাটের ওপরে বসেছেন মাত্র, আর তখনই শাবকটি ঘুমের মধ্যেই লাফ মারে। কোমরে ভর দিয়ে জজ হাসানের মুখোমুখি বসে বিস্কুটগুলোর দিকে তাকিয়ে লেজ নাড়ে। অভিমান ভরা ছোট ছোট চোখ দিয়ে একবার জজের দিকে তাকায়, আর একবার বিস্কুটগুলোর দিকে তাকায়। ওকে একা রেখে নাস্তার আয়োজনে এই অভিমান! ‘অধিকার! অভিমান!’ জজ হাসান হেসে উঠে হাত বাড়াতেই শাবকটি লাফিয়ে তার কোলে ওঠে।” স্ত্রী মারা যাওয়ার পর একাকী নিঃসঙ্গ বৃদ্ধের যাবতীয় মন ও শরীরস্থিত অসুস্থতার জায়গার দখল নেয় কুড়িয়ে পাওয়া এই ছোট্ট শাবকটি। “কানাডায় মেয়ে, ভার্জিনিয়ায় ছেলে এখন টেনশন ফ্রি।” দেশে থাকা বড় ছেলে যার সঙ্গে দুবছরে দুবার দেখা হয় জজ হাসানের তারও খুব টেনশন তার বাবাকে নিয়ে। চন্দন এক মুহূর্তে পাঠককে পৌঁছে দেন এক সফল মানুষের অন্দরমহলেÍযাঁর ছেলে মেয়ে দেশে এবং বিদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত। যাঁর ছেলে মেয়ে বাবার জন্য ভীষণ চিন্তিত। যাঁর সন্তানরা নিয়মিত বাবার খোঁজখবর নেয় স্কাইপ-মাধ্যমে। তবু সেই সফল মানুষটির কিসের যেন অভাববোধ, কিসের যেন ‘অসুখ’! পাঠক নিশ্চিত জানে অসুখ ঠিক কোথায়! সেও যে ততক্ষণে হাতড়ে মরছে নিজের অন্দরে! একইরকমভাবে ‘নিজের দিকে দেখি’ গল্পটি পড়তে পড়তে চন্দনের পাঠিকারাও যে সেঁজুতির মধ্যে নিজেদেরই খুঁজে পান। যে দোলাচলে পড়ে সেঁজুতি সাহায্য চায় তার স্বামী চয়নের কাছে, তার নিজের মায়ের কাছে, সেই দ্বন্দ্বের সঙ্গে সমঝোতায় এমন অনেক ‘সেঁজুতি’কেই আসতে হয়েছে। মাস্টার্স পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়ে পিএইচডি করার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে সেঁজুতি। এমন একটি সময় তাকে সন্তানের বন্ধনে জড়িয়ে ফেলার অর্থ তার স্বপ্নকে ভেঙে চুরমার করে দেওয়া, ঠিক যে কাজটি করে তার স্বামী চয়ন। সে অ্যাবোরশনের অনুরোধ করলে তাকে হত্যাপরাধী হিসেবে তুলে দেওয়া হয় কাঠগড়ায়। গল্পের শেষ লাইনে লেখক জিতিয়ে দেন সেঁজুতিকেÍ“চূড়ান্ত অবহেলা আর মর্মান্তিক অপমানের সুতীব্র যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে বিনিদ্র রাত কাটিয়ে ঠিক সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সেঁজুতি এই চরম ও অলঙ্ঘনীয় সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছল যে, সে মা হবে এবং চয়নকে ডিভোর্স দেবে।” পাঠকের চোখ অজান্তেই কখন যেন ঝাপসা হয়ে আসে! ঠিক একইরকমভাবে ‘সুখ স্বপ্নের দিন’ গল্পের শেষেও চমকে ওঠে পাঠক, ঝাপসা হয়ে আসে চোখÍ“ওদের কচি দুটি শরীরের ওপর দিয়ে গিয়েছে কিনা ট্রাকের সামনের চাকা দুইটাÍছোট্ট দুটি দেহে এতো মাংস এতো রক্ত ছিল, ছোট্ট দুটি মাথায় এতো মগজ ছিল, আমার এই দুই হাতে জমিয়ে কুড়িয়ে কুল পাচ্ছিলাম না, কারা যেন তুলে নিয়ে গেল তোমাকে, আমি ছেলেমেয়ের হাড়-মাংস-মগজ-রক্ত জমা করছি, ছেলে-মেয়েকে আলাদা করছি না, আমারই তো শরীর, আলাদা করব কেন?” অথচ গল্পের শুরু হয় প্রফেসর হোসেনের ‘আড়াই মিনিটের নিশ্বাসরুদ্ধ ব্যস্ততা শেষে প্রায় লাফিয়ে’ বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়া দিয়ে। তিনি তখন মশগুল সুখ-স্বপ্ন দেখার চিন্তায়। রহস্যের জাল তৈরি করে পাঠককে সেই গোলকধাঁধায় আটকে ফেলা চন্দনের লেখার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট। এই সুখ-কল্পনা যে আসলে যন্ত্রণা ভুলে থাকার চেষ্টা, ‘এসকেপিসম’ তা বুঝতে তাই একটু সময় নেন পাঠক। খুব যত্ন করে, মায়ায় জড়িয়ে, পেলব অনুভূতির বাঁধনে চন্দন নির্মাণ করেন জজ হাসান, প্রফেসর হোসেন এবং সেঁজুতিকে।
‘কতিপয় অনাথ শিশু’ ও ‘আমৃত্যু শ্বাসকষ্ট’ গল্পদুটি লেখক হিসেবে চন্দনের প্রবর্ধনের সাক্ষর বহন করে। দুটি গল্পেই রাষ্ট্রযন্ত্রের অনিয়ন্ত্রিত উচ্চাকাঙ্খার স্বীকার হতে হয় ‘সৈকত’ এবং ‘মাজহার’কে। সৈকত রাষ্ট্রের নির্দেশে গুলি চালায়। নিরাপত্তা বাহিনীর কিলিং স্কোয়াডের সৈনিক হিসেবে মানুষ খুন করে রোজ। একজন মানুষ খুন করতে একটির বেশি গুলি কখনই খরচ করতে হয়নি তাকে। সে সাশ্রয়ী। কিন্তু আত্মগ্লানির বোঝা বয়ে বেড়ানোর মতো চওড়া কাঁধ তার নয়। বিসমিল্লা শব্দের বা নিয়মিত নামাজ পাঠের ঠুলি চোখে পরে সে তার কাজকে ন্যায্যতা প্রতিপাদনের চেষ্টা করেÍ“এখন আমি নিয়মিত মানুষ খুন করছি এবং ধর্মে মন দিয়েছি”। তবে প্রায় বছর দশেকের নাছোড় চেষ্টার পর তার বউ সোহেলি মা হতে চলেছে এই খবরে তার ভিতরের উত্তাল ঢেউ তাকে কতিপয় অনাথ ও অভিভাবকহীন শিশুর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেয়। অন্যদিকে মাজহার রাষ্ট্রের ষড়যন্ত্রের শিকার। মাজহারের মতো সৎ, স্বপ্নসন্ধানী কিন্তু স্বপ্ন পূরণ করতে অসমর্থ মানুষদের রাষ্ট্রের ভারি পছন্দ। তাঁরাই যে সহজ শিকার। একটি সরকারি ফ্ল্যাট, বসের গাড়ি চেপে পরিবার নিয়ে নববর্ষের দিন ঘুরতে যাওয়ার আনন্দ, বসের যেচে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ ও কাঁধে হাত রেখে খোশগল্পÍমাত্র এতোটুকুর বিনিময় মূল্য মাজহারের জীবন, তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার দিশাহীন ভবিষ্যত এবং হাজার হাজার আঠেরো-উনিশের ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা!! হায়রে অবোধ স্বপ্ন!! মেডিকেল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস কান্ডের অন্যতম নায়ক মাজহারের ‘লজ্জা’ (রাষ্ট্রের নয়!) লেখক ততক্ষণে ছড়িয়ে দিয়েছেন অগণিত পাঠকের বুকে। ‘মৃত্যু বিষয়ক কবিতা প্রেমী’ ও ‘আদিম কাব্যকার’ চন্দনের লেখা এমনই আরও দুটি বিচিত্র স্বাদের গল্প।
ভালোবাসার গল্পও বলেন চন্দন। এমন এক আচ্ছন্ন করে রাখা ভালোবাসা যা শাহিনাকে তার পেছনে ফেলে আসা জীবনের ঘোর কাটিয়ে উঠতে দিল না বাকিজীবন। ‘পল্লীবালিকার সুখ-শাস্তি’ গল্পে ক্লাস নাইনের শাহিনা তুমুল ভালোবেসেছিল কলেজে পড়া বড়লোকের ছেলে বশিরকে। এক বৈশাখের কাঠফাটা রোদে কাঁচা আমের গন্ধে নিদারুণ শরীরী উত্তাপে ভেসে গিয়েছিল দুজনে। সেই থেকে বৈশাখ পড়লেই শাহিনা দগ্ধ হতে থাকে ভিতরে ভিতরে। মানিক অনেক ভেবেও কূলকিনারা পায়নি, কেন!! মানিক তার স্বামী। শাহিনার সাধ পূরণ করতে না পারার অক্ষমতা তাকে তাড়া করে ফেরে। সেই অক্ষম আক্রোশে শাহিনার গায়ে হাত তোলে সে, মেরে ফাটিয়ে দেয় ঠোঁট। শাহিনা জানতেও পারল না ওই ফাটা ঠোঁটের রক্তের মধ্যে দিয়েও ভালোবাসা বহমান ছিল। মানিকের পক্ষে হয়ত বশির হওয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু ভালোবাসার বিচিত্র পথে হেঁটেছিল সেÍনিজের কিডনির বিনিময়ে সে তার বস্তির ঘরে বয়ে এনেছিল কচি আমের মতো রঙের একটি ফ্রিজÍশাহিনার যে বড়ো সাধ ছিল! শাহিনা অবশ্য ততক্ষণে সেই বুড়ো আমগাছটার পেটের ভিতরে গুটিশুটি মেরে শুয়ে নিজের কলিজা সঁপে দিয়েছে সার সার কাঠপিঁপড়ের কাছে!!
এই তিরিশটি গল্প পাঠককে এক সুতীব্র দহন জ্বালায় দগ্ধ করে। পাঠকের কাছে পৌঁছে দেয় সেই সঙ্কটের বিপন্নতা যার ভার বয়ে বেড়াচ্ছেন লেখকÍযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতির কঠিন সময়ে যে সঙ্কট ভালোবাসার, আদর্শের, মতবাদের, বিশ্বাসের, ইতিহাসের, গনতন্ত্রের এবং সর্বোপরি এক সদ্যোজাত দিশাহীন রাষ্ট্রের। তবু সংগ্রাম ও স্বপ্ন ক্ষান্ত হয় নাÍ“তুমি সম্পূর্ণ ভূমিসাৎ হওয়ার আগে তোমার মশাল নিতে প্রস্তুত/ শতছিদ্র ভাই বোনেরা/ তারা পরপর সময়ের সীমান্ত পায়ে দলে এগোবে, / ততক্ষণ চলুক তোমার লড়াই/ শূন্যতার বিরুদ্ধে”।
‘ত্রিপাদ ঈশ্বরের জিভ’ এই শেষ গল্পটিতে বিষ্ণু কামার যেন পৃথিবীজুড়ে সেই সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি। বিষ্ণু কামারের জিভ যেন সমস্ত স্বাধীনতাকামী মানুষের বাক-স্বাধীনতার প্রতীক। নৈরাজক রাষ্ট্রের ক্ষমতার অপপ্রয়োগের বিরুদ্ধে জেহাদ। বিপন্ন অধিকার ফিরে পাওয়ার লড়াই। ভয়হীনভাবে। ড. ফেরদৌসের হাতে বিষ্ণুকামার সঁপে যান সেই প্রতিবাদের উত্তরাধিকার। আর নতুন সূর্যের প্রত্যাশায় ইতিবাচকভাবে শেষ হয় এই সংকলন।
লেখকের নিজের কথায়, “লেখালেখির হাত মকশো হয়েছিল দেয়াল পত্রিকায়”, তবে দেওয়াল থেকে কাগজের পাতায় পৌঁছানোর এই জার্নি নিঃসন্দেহে স্বপ্নাতীত। লেখক যা পরিবেশন করেন তা কনটেন্ট আর তার আধার, ভাষা। এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সাথে সাথে চন্দনের ভাষার ব্যবহারও প্রশংসার্হ। জারি থাকুক তাঁর এই চলমান অন্বেষণ, এই চিরন্তন মানসিক পথচলা।
* সুমনা ভট্টাচার্য : পশ্চিম বাংলার লেখক ও শিক্ষক।


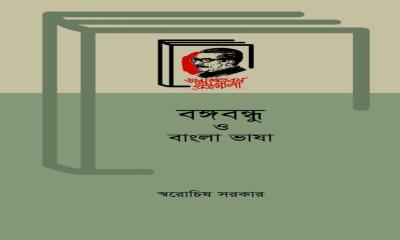












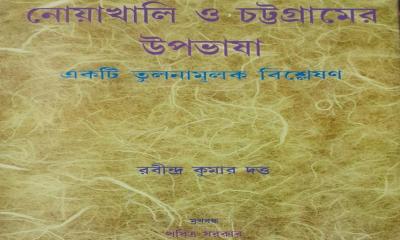



আপনার মতামত লিখুন :